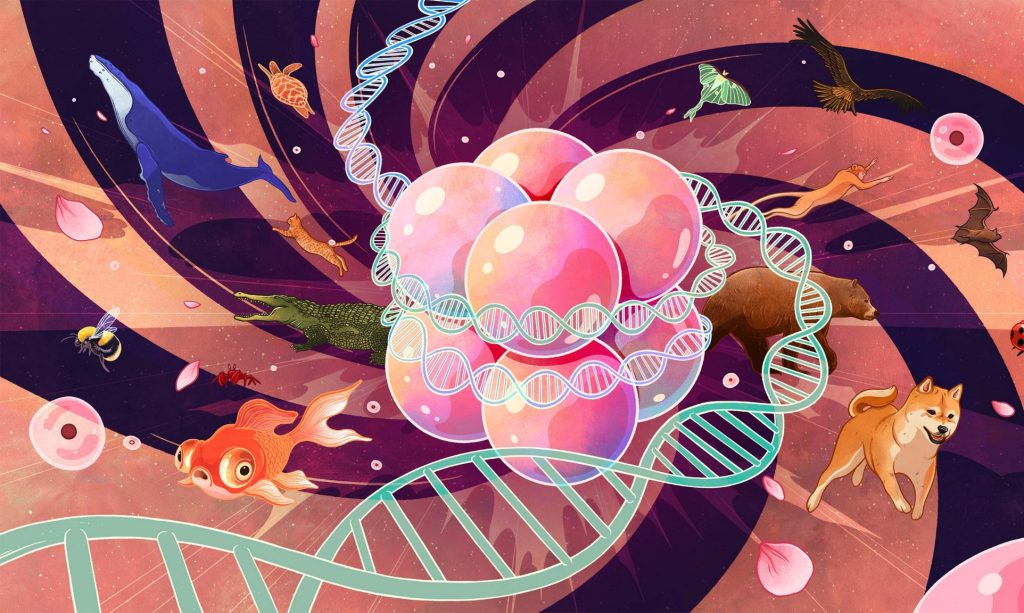
আমাদের শরীরে লক্ষ কোটি কোষ আছে। একটা কোষ থেকে বিভাজন হয়ে দুটো কোষ হয়, ইংরিজিতে তাদের নাম মাদার সেল আর ডটার সেল। এমনিতে ডটার সেল ঠিক মাদার সেলের মতো হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে কঠিন ব্যাপার আছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কোষগুলো সব একরকম। লিভারের কোষ বিভাজন হয়ে লিভারের কোষই হয়, কিডনির কোষ বিভাজন হয়ে কিডনির কোষই হয়, এই লেখাটা সেই বিষয়ে।
আমাদের প্রতিটা কোষে ডিএনএ থাকে, ডিএনএর মধ্যে থাকে জিন, জিন থেকে প্রোটিন তৈরী হয়, এবং প্রোটিনগুলোই আমাদের কোষের মধ্যে সব কাজ করে, অনুঘটক (ক্যাটালিস্ট) হিসেবে। আমাদের কোষগুলো তো আসলে রাসায়নিক কারখানা, অনেক রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে হলে অনেকসময় তাপ লাগে। কারণ বিক্রিয়াতে যেসব অনু অংশ নেয়, তাদের কাছাকাছি আসতে হয়। কিন্তু শরীরের তাপ বাড়লে আমরা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই প্রোটিনরা এই বিক্রিয়ার অণুগুলোকে ধরে কাছাকাছি আনে, কম তাপেও । তাই প্রোটিনরা অনুঘটক।
কিন্তু মুশকিল হলো, আমাদের প্রতিটা কোষের ডিএনএতে প্রায় ২৫০০০ জিন আছে। এই ২৫০০০ জিনের থেকে যদি ২৫০০০ রকমের প্রোটিন তৈরী হয় সব কোষে, তাহলে কোষের মধ্যে ভিড় খুব বেড়ে যাবে, প্রোটিনরা তাদের কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে পারবে না, আর সব কোষে সব প্রোটিনের প্রয়োজনও নেই। যেমন লিভারের কাজ হলো রক্ত থেকে দূষিত জিনিস পরিষ্কার করা, রক্তে শর্করার পরিমান নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। লিভারে তো মস্তিষ্কের প্রোটিনের কোনো কাজ নেই, সুতরাং মস্তিষ্কের প্রোটিন লিভারে শুধু ভিড় বাড়াবে, একেবারেই ভালো কথা নয়। উপায়টা কি তাহলে?
উপায়টা বুঝতে গেলে আমাদের একটু বুঝতে হবে কোষে ডিএনএ কিভাবে থাকে। কোষের বেশির ভাগ ডিএনএ, প্রায় ৯৯%-ই, থাকে একটা ছোট্ট জায়গায় যাকে বলে নিউক্লিয়াস। আমাদের ডিএনএ প্রায় ৩ মিটার লম্বা, তাকে ওই ছোট্ট জায়গায় ঢোকানো সহজ ব্যাপার নয়। এ যেন অরিগামি – জাপানি কাগজ মোড়ার শিল্প। এই ডিএনএকে নিউক্লিয়াসে ঢোকানো হচ্ছে সব থেকে কঠিন অরিগামি। সেটা কিভাবে হয় খুব সহজে বলতে গেলে, ভয়ঙ্কর ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। এক ধরণের প্রোটিন আছে, যাদের হিস্টোন প্রোটিন বলে। ডিএনএ তো একটা লম্বা চেনের মতো, চারটে বেস দিয়ে তৈরি, আডেনিন, গুয়ামিন, সাইটোসিন আর থায়ামিন,এই ডিএনএ চেনটা হিস্টোন প্রোটিনগুলোর ওপর পেঁচিয়ে থাকে। কয়েকটা হিস্টোন প্রোটিন মিলে নিউক্লিওসম, তাকে পেঁচিয়ে ১৫০ টা ডিএনএ বেস, এইরকম একের পর এক। সেগুলো আবার আরো পেঁচিয়ে থাকে- যা আমরা এখনো ভালো করে বুঝতে পারি নি, গবেষণা চলছে এই নিয়ে।
ডিএনএ র ছবি আমরা সবাই দেখেছি। সেটা আসলে খোলা ডিএনএ, নিউক্লিয়াসে ডিএনএ ঐ রকম খোলা থাকে না। ডিএনএ থেকে প্রোটিন তৈরী করতে হলে প্রথমে ডিএনএ- কে খুলতে হয়, তারপর তার একটা কপি করতে হয়। এই কাজ করার জন্যে ভীষণ দরকারি একদল প্রোটিন আছে, তাদের বলে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। তারা এই কাজ করতে পারে একমাত্র যদি তারা নিউক্লিয়াসে ঢুকতে পারে। যদি ডিএনএ খুব টাইট ভাবে নিউক্লিওসমে জড়িয়ে থাকে, তাহলে তারা সেই ডিএনএর নাগাল পায় না, আর সেখানে কোনো জিন থাকলে তার থেকে প্রোটিন তৈরী করতে পারে না। এইবার বোঝা যাচ্ছে রহস্যটা। লিভার কোষে যে যে প্রোটিন লাগে, সেখানকার ডিএনএ একটু আলগা করে দিতে হবে, যাতে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টররা ঢুকতে পারে, আর যে প্রোটিন লাগে না, সেখানকার ডিএনএ টাইট করে রাখতে হবে। কিন্তু কিভাবে?
আমরা ভাবি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি – এইসব বিভিন্ন বিষয়। এটা কিন্তু একটু ভুল । এদের মধ্যে অনেক যোগসূত্র আছে। ডিএনএ হচ্ছে একটা ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী অণু, এর মধ্যে একটা ফসফেট গ্ৰুপ থাকে, তার একটা নেগেটিভ চার্জ থাকে। এই জন্যেই ডিএনএ হিস্টোন প্রোটিনে জড়িয়ে থাকে। এই নেগেটিভ চার্জ যদি আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ডিএনএ আরো শক্ত ভাবে হিস্টোনে জড়িয়ে থাকবে, আর চার্জ কমিয়ে দিলে, নেগেটিভ চার্জটাকে একটা পসিটিভ চার্জ দিয়ে শূন্য করে দিলে, ডিএনএ আলগা হয়ে যাবে। নেগেটিভ চার্জ বাড়ে যখন একটা মিথাইল গ্রুপ হিস্টোন প্রোটিনে গিয়ে লাগে। আর এসিটাইল গ্রুপ চার্জ শূন্য করে দেয় |
কোষ বিভাজনের সময় মাদার সেলে যে যে হিস্টোনে মিথাইল গ্রুপ লেগে থাকে, ডটার সেলেও সেখানে মিথাইল গ্রুপ লেগে যায়। তাই সেল মায়ের মতো হয়, মানে মা যা যা প্রোটিন তৈরী করে, মেয়েও তাই করে।
ব্যাপারটা আমি খুব সহজ করে লিখেছি, আসলে এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে তো, বায়োলজির মধ্যেও অনেক ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি ঢুকে আছে। এপিজেনেটিক্স আরো বিরাট বিষয়, জিন থেকে প্রোটিন তৈরী আরো অনেক রকম ভাবে বন্ধ করা যায়, সেসব গল্প অন্যদিন করবো।

অসাধারণ লেখা বিশেষ করে আমার মত সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করার জন্য
এত প্রান্জল করে বোঝানো এই জটিল বিষয় যে আমার মত অজ্ঞ লোকেরও পড়তে ভালো লাগে ।