মাকে আমরা ‘তাই’ বলে ডাকতাম [মরাঠিতে বাড়ির মেজো মেয়েকে এই নামে ডাকা হয় – অনুবাদক]
বাবা-মার কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু শিখে নেয়; ‘তাই’য়ের কাছ থেকে আমি কী শিখে নিয়েছিলাম? শিখেছিলাম নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনটা! তিনি ছিলেন একজন সুসংগঠিত মানুষ, কেবল তাঁর নিজের দৈনন্দিন ধরাবাঁধা কাজকর্মর ব্যাপারেই নয়, তাঁর পরিচালনাধীন গোটা সংসার সম্বন্ধেই। কোনো অতিথি এসে পড়লে কোনো কিছুর যাতে ঘাটতি না পড়ে, সে ব্যাপারে তিনি সাবধান থাকতেন। ব্যয়বরাদ্দর সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তিনি নতুন নতুন উদ্ভাবন করতেন। … মারাঠিতে একটা কথা আছে যাতে বলা হয়, বেয়াক্কেলে লোক হল সেই যে তেষ্টা পেলে কুয়ো খুঁড়তে বসে। ‘তাই’ কিন্তু একটা নয়, তিন-তিনটে কুয়ো আগে থেকে খুঁড়িয়ে রাখতেন, তেষ্টা পাওয়ার অপেক্ষা করতেন না।
আমার ছোটোবেলার সবচেয়ে সুখের স্মৃতি হল শোবার সময় তাইয়ের গল্প পড়ে শোনানোর। তাঁর ঝুলিটি অজস্র ইংরেজি, হিন্দি আর মরাঠি গল্পে ঠাসা ছিল। তিনি কিন্তু হিন্দি আর ইংরেজি সব গল্পই চটজলদি মরাঠিতে অনুবাদ করে শোনাতেন। অবশেষে তিনি আমাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সফল হলেন, আমরা নিজেরাই বই পড়তে লাগলাম। সংসারের অজস্র ঝক্কি সামলানোর পর কী করে যে তিনি আমি ও আমার ছোটো ভাই অনন্তর জন্য এই পরিমাণ সময় আর শক্তি খরচ করতেন, যাতে আমরা লেখাপড়ায় কোনোদিক থেকেই পিছিয়ে না পড়ি, তা ভাবলে অবাক লাগে।
বলা হয়ে থাকে যে, সাধারণত ছেলেরা তাদের বাবার ভাবমূর্তিকে আদর্শ করে বেড়ে ওঠে। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না, তবে আমার বাবার (বিষ্ণু বাসুদেব নারলিকর [১৯০৮-১৯৯১], বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রফেসর, ১৯৮১-৮২তে ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি) গোটা জীবৎকাল ধরেই আমি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেছিলাম। বাবা ছিলেন এক অসাধারণ শিক্ষক। যারাই তাঁর কাছে পড়েছে, তাদের মনে তিনি স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ভারত ঘুরতে গিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর পুরোনো ছাত্রদের দেখা হত। দেখতাম, তারা সকলেই তাঁকে কী গভীর শ্রদ্ধা করত। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র নিয়েও সেই একই কথা। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে একেবারে প্রথম দিকে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। যেসব ছাত্রদের তিনি তৈরি ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাদের দৌলতেই বেনারস আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। বাবা মেঝেতে মাদুরের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন, তাঁর চতুর্দিকে তাড়া তাড়া অঙ্কর কাগজ ছড়ানো – এ ছবিটা আমার মনে আজও টাটকা।
তবে বাবার যে-গুণটা আজকের দিনে বিরল হয়ে উঠেছে, তা হল তাঁর অখণ্ড সততা। শত চাপ আর প্রলোভনের মুখেও তিনি একটা ন্যায্য সিদ্ধান্ত থেকে নড়তেন না। এই গুণটির জন্য তিনি রাজস্থান রাজ্যর সরকারের কাছে খুবই সমাদৃত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজস্থান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধান। পদটি ছিল খুবই স্পর্শকাতর ও প্রভাবশালী। বেঠিক লোকের হাতে পড়লে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। বাবার আগে সেই ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর আমলে ওই সংস্থা একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি অর্জন করে। সততা, সুবিচার, এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতার জন্য সংস্থাটি নাম কিনেছিল।
১৯৬৪-র জুনে রয়্যাল সোসাইটির অধিবেশনে আমি আর ফ্রেড হয়েল যে-নতুন অভিকর্ষ তত্ত্ব পেশ করি তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এই কাজটা করে আমি গভীর বৌদ্ধিক তৃপ্তি পেয়েছিলাম, কেননা এর মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্বর সঙ্গে মাখ-এর জাড্য বিষয়ক ভাবনাচিন্তার একটা সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা গিয়েছিল। আইনস্টাইন, যিনি একদা এর্নস্ট মাখ-এর গুণমুগ্ধ ছিলেন, তিনি নিজেই চেষ্টা করেছিলেন ওরকম একটা যোগসূত্র বার করতে, কিন্তু পারেননি। কারণ মাখ-এর যুক্তি ছিল, এমন একটা দূর পাল্লা অব্দি বিস্তৃত ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকতে হবে যা যেকোনো কণাকে জাড্যধর্ম দান করবে। যেমন এক টুকরো পদার্থর একটা ভর আছে, কিন্তু তার দরকার এমন একটা বল যা তার বিরাম-দশা বা সমগতির চলন-দশা (নিউটনের প্রথম গতিসূত্র) বদলে দেবে, যেহেতু পদার্থটি এমন এক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান যা পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। মাখ-এর এই ধারণাটি কখনো স্পষ্ট করে পরিমাণাত্মক ভাষায় ব্যক্ত হয়নি। এ ধারণাটি মানতে আইনস্টাইনের অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ দূরপ্রযুক্ত ক্রিয়ার ধারণাটি এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছিল, যার প্রবর্তক নিউটন। ওই ধারণাটিকে কাজে লাগিয়েই কুলম তড়িৎ ও চৌম্বক বলের ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতেই ওই ধারণাটির বদনাম রটতে থাকে।
‘মাখ-প্রান্ত’ থেকে শুরু করে জাড্যর সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে আমাদের সমীকরণগুলো যখন আমাদের পৌঁছে দিল অভিকর্ষর এক তত্ত্বে, তথাকথিত ‘আইনস্টাইন-প্রান্তে’, তার রোমাঞ্চ আমরা দুজনেই কীভাবে যে অনুভব করেছিলাম, সে আমার আজও মনে পড়ে! দেখা গেল, অভিকর্ষ সমীকরণগুলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সমীকরণগুলোর চেয়েও বেশি সার্বিক, কিন্তু আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো যে এই সমীকরণগুলোরই বিশেষ সীমিত রূপ, সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম। রয়্যাল সোসাইটিতে আমরা এই কাজটাই উপস্থাপন করেছিলাম।
কিন্তু এটা আপনাতে-আপনি সম্পূর্ণ একটা লক্ষ্য ছিল না। আরো অনেক পথ চলা আমাদের বাকি ছিল। ১৯৬৭-৭২ পর্বে আমরা দূরপ্রযুক্ত ক্রিয়ার কোয়ান্টম বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলাম। আর, অতি সম্প্রতি আমরা দেখাতে পেরেছি যে অতিক্ষুদ্র কোয়ান্টাম পরিঘটনা (ফেনোমেনা) অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ডর অতিবৃহৎ কাঠামোটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার আরো মনে হয়, কোয়েসার আর গ্যালাক্সিগুলোর লাল-অপসরণ সংক্রান্ত যেসব রহস্যময় ফলগুলিকে সার্বিক আপেক্ষিকতার তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে ধরানো যাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে, আমাদের অভিকর্ষ তত্ত্ব হয়তো সেগুলোর ওপর আলোকপাত করতে পারে।
কেম্ব্রিজে আমার গবেষণা-পর্বর আরেকটি বলবার মতো ঘটনা হল, ফ্রেড হয়েল কর্তৃক ‘ইনস্টিটিউট অব থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রনমি’ (এখনকার ‘ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রনমি’)-র পত্তন। অ্যাস্ট্রনমির পুনরুত্থানের ঘটনাটি আগে থেকে আঁচ করে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে হয়েল কেম্ব্রিজে এ বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ওপর জোর দেন। কিন্তু কেম্ব্রিজের অ্যাস্ট্রনমি চর্চার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে রাজনৈতিক কারণে নতুন কেন্দ্রটি স্থাপিত হল সদ্য-স্থাপিত সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর সপক্ষে প্রদত্ত একটা যুক্তি ছিল, সাসেক্স-এর হার্স্ট্মন্সোয় রয়্যাল গ্রিনিচ অবজার্ভেটরির কাছাকাছি হওয়ায় কেন্দ্রটি উপকৃত হবে। হয়েলকেই এর প্রধান হবার জন্য আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি রাজি হননি। তিনি কেম্ব্রিজেই একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। সরকারি সাহায্য না পেয়ে তিনি বেসরকারি ফাউন্ডেশনগুলির দ্বারস্থ হলেন। নাফিল্ড এবং ওলফসন ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে তিনি ১৯৬৬ সালে ইনস্টিটিউট অব থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রনমি গঠন করতে সমর্থ হলেন। ইংল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় টাটকা হাওয়ার ঝলক এনে দিল এই প্রতিষ্ঠান এবং দেখতে না দেখতে আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি অর্জন করল। তার খ্যাতি এতটাই বাড়ল যে ১৯৮০-র দশকের শেষে দিকে যখন খরচ কমানোর তাগিদে রয়্যাল গ্রিনিচ অবজার্ভেটরি ঠিক করল, তারা হার্স্ট্মন্সো থেকে দেশের অন্য কোথাও সরে যাবে, তারা বেছে নিল সেই কেম্ব্রিজকেই, যাতে করে হয়েলের প্রতিষ্ঠানের ঠিক পাশে থাকা যায়।
উৎস: Jayant V. Narlikar, My Tale of Four Cities: An Autobiography, National Book Trust, India, New Delhi, 2016. আংশিক বাংলা অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী
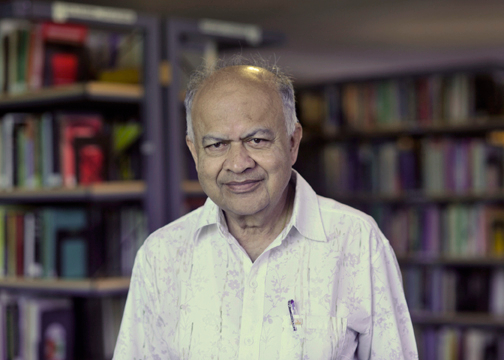
মোটের উপর তাঁর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। চমৎকার ঝরঝরে অনুবাদ হয়েছে। আমাদের সকলের, বিশেষ করে ছাত্রাছাত্রীদের এইরকম একটা মানুষের জীবনী পড়ে অনুপ্রেরণা জাগতে পারে।