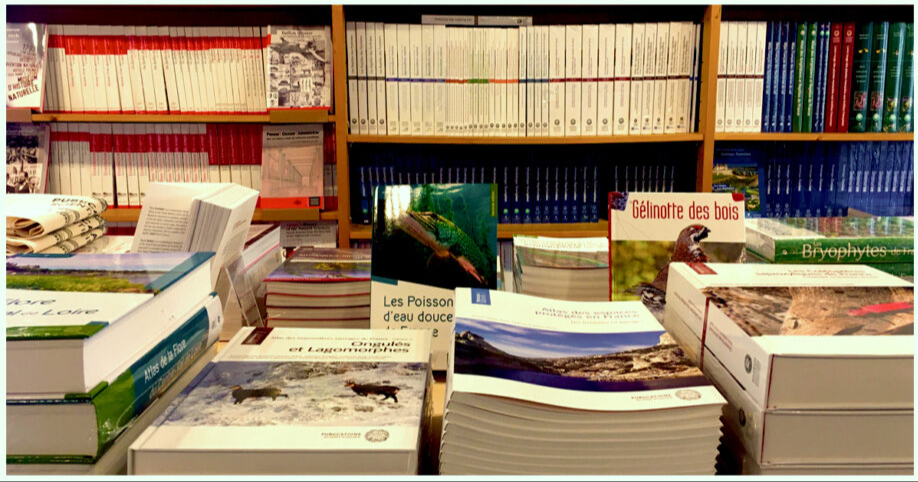
ইদানীং সংরক্ষণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত বহু বিজ্ঞানীর মনে হচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব থেকে শুরু করে আস্ত আস্ত বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গঠিত এই বিশাল পৃথিবীর যে-জীববৈচিত্র্য, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের কৃষ্টি আর ভাষার বৈচিত্র্য। ২০১২ সালে প্রোসিডিংস অব ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, জীববৈচিত্র্যে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতেই বিশ্বের ৭০% ভাষা ব্যবহৃত হয়। এইসব ভাষার অনেকগুলিই একেকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ নানান এলাকা্র বিপন্ন প্রজাতিগুলিরই মতন, এই ভাষাগুলিও বিলুপ্তির মুখে। আর স্থানীয় ভাষা বিলুপ্তির অর্থ অমূল্য সব বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানেরও বিলুপ্তি।
জীববৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলির হিসাব করলে দেখা যাবে ভাষা এ ক্ষেত্রে একটি বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। ‘কনসার্ভেশন বায়োলজি’ পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি অধ্যয়নপত্রে দেখানো হয়েছে, ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লিখিত সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি এক নাগাড়ে অবহেলিত হয়। তাঁরা ৫০০টি ইংরেজি গবেষণাপত্র নিয়ে সমীক্ষা করে দেখেছেন। এগুলি সবই উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত। পত্রটির প্রধান লেখক কেলসি হানা এবং অন্যান্য গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত গবেষণাপত্রগুলি নিজ নিজ ভাষায় প্রচুর উল্লেখিত হলেও, অন্যান্য ভাষায় তাদের উল্লেখ খুব কম। এর কারণ হচ্ছে, ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় লিখিত এইসব গবেষণাপত্রগুলি বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে না, তাঁরাও এসবের খোঁজ করার দরকার বোধ করেন না। ভাষার প্রতিবন্ধকতা এমনই। যেমন প্রাচ্য সারসের ওপর জাপানি ভাষায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানি অনেক গবেষণাপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য কোনো ভাষায় রচিত গবেষণাপত্রে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। অথচ ওই প্রজাতিটি শুধু জাপানে নয়, চীনে, রাশিয়াতে আর কোরিয়াতেও বিপন্ন। অধ্যয়নপত্রটির আরেক লেখক তাৎসুয়া আমান বলেছেন, পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্যর অনেকটাই এমন সব অঞ্চলে ঘনীভূত যেখানে ইংরেজি প্রাথমিক ভাষা নয়। তাই ওইসব অঞ্চল সম্বন্ধে খোঁজখবর না নিয়ে, কিংবা ওইসব স্থানীয় বিশেষজ্ঞতার সাহায্য না-নিয়েই সিদ্ধান্ত নিলে গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রয়াস ব্যাহত হতে বাধ্য।
এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, অন্য ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিলেই সেগুলির উল্লেখ-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই বিশ্লেষকরা বলছেন, অন্য ভাষার লেখকদের ভাবা উচিত কীকরে তাঁদের লেখা ইংরেজি-ভাষীদের কাছে পৌঁছয়, আবার ইংরেজি-ভাষী বিজ্ঞানীদেরও উচিত নিজেদের দিগন্তকে প্রসারিত করা। তাঁদের উচিত এগিয়ে এসে অন্যান্য ভাষায় উপস্থাপিত জ্ঞানসম্ভারের সন্ধানে রত হওয়া। তাহলেই যাবতীয় প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণকে একসঙ্গে বিবেচনা করা সম্ভব হবে।
“The University of Queensland, as part of the Wiley – The University of Queensland agreement via the Council of Australian University Librarians.”
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70051?et_cid=5622511&et_rid=1119437874#:~:text=The%20University%20of%20Queensland%2C%20as%20part%20of%20the%20Wiley%20%2D%20The%20University%20of%20Queensland%20agreement%20via%20the%20Council%20of%20Australian%20University%20Librarians.
