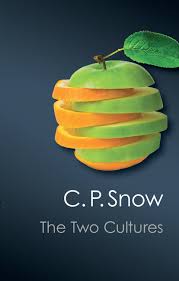
১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যিক সি.পি.স্নো এর একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী বক্তৃতা ওই বছরেই বই আকারে দুটি পর্বে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্বটি ‘দ্য টু কালচার্স’ এবং দ্বিতীয় পর্বটি হল ‘সায়েন্টিফিক রেভোলিউশন’।
‘দ্য টু কালচার্স’ নিবন্ধের উপজীব্য ছিল কলা এবং বিজ্ঞান দুটো ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভাগ হয়ে পড়া এবং এই বিভাজন কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের কাছেই পৃথিবীর সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠা।
১৯৫৯ সালের ৭ই মে কেমব্রিজ সেনেট হাউসে রাখা এই বক্তব্য পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। স্নোয়ের এই বক্তব্য এবং বই দুটিই ৬ই অক্টোবর ১৯৫৬ তে ‘নিউ স্টেটসম্যানে’ ওই একই নামে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পরিবেশনা।
বই আকারে প্রকাশ হওয়ায় আতলান্তিকের দুই পারেই স্নোয়ের এই বক্তব্য বহুল পাঠিত ও আলোচিত হয়, যা স্নোকে ১৯৬৩ সালে মূল লেখাটির একটি অনুসারিত সংস্করন ‘দ্য টু কালচার্স: অ্যান্ড এ সেকেন্ড লুক: অ্যান এক্সটেন্ডেড ভার্সান অফ দ্য টু কালচার্স অ্যান্ড দ্য সায়েন্টিফিক রেভোলিউশন’ লেখার উৎসাহ যোগায়।
স্নোয়ের বইতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় সেই ভিক্টোরিয়ান আমল থেকে চলে আসা কলা বা সাহিত্যের বিষয়গুলিকে, এমনকি বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার বিনিময়ে, অতিপ্রাধাণ্য দেওয়ার রীতির সমালোচনা করা হয়। বাস্তবিকই এই রীতির ফলস্বরূপ ব্রিটিশ অভিজাত সমাজ (রাজনীতি, প্রশাসন এবং শিল্প) আধুনিক বিজ্ঞান চালিত সমাজকে সামলানোর উপযুক্ত প্রস্তুতি থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে এর বিপ্রতীপে, স্নো বলেন, জার্মানি এবং আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিল তার নাগরিকদের বিজ্ঞান এবং কলাবিভাগের বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী করে তুলতে, এবং উন্নততর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কদের এই বিজ্ঞানচালিত যুগে পাল্লা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকরী করে তোলে।
যদিও স্নোয়ের এই চিন্তাধারা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। কলাবিভাগের অনেক সাধক ওনার সাথে ভিন্নমত পোষন করেন। আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও কলাবিভাগের এই বিভাজন বর্তমান?
