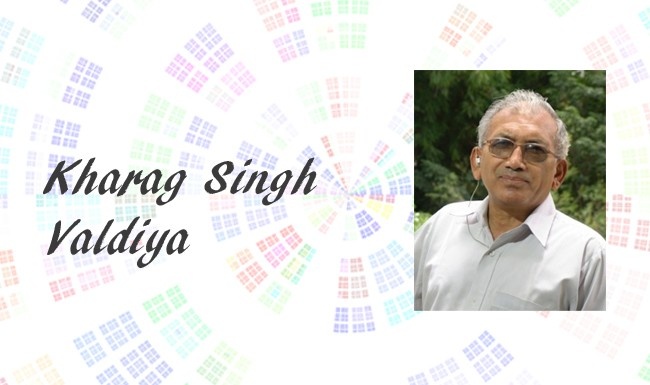
পর্ব-১
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
খড়গ সিং ভালদিয়া ছিলেন ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিকদের মধ্যে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। হিমালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও পরিবেশ নিয়ে তাঁর অগ্রণী কাজের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তিনি তাঁর গবেষক জীবনের প্রায় ৪০ বছর ধরে হিমালয় পর্বতের ভূ-তত্ত্ব নিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। হিমালয়ের স্তরবিন্যাস, গঠন এবং ভূ-গাঠনিক বিবর্তন নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিমালয়-সংক্রান্ত বহু চলমান গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে।
হিমালয় পর্বতমালা পৃথিবীর সবচেয়ে নবীন ভঙ্গিল পর্বত। অর্থাৎ, প্রায় ৫ কোটি বছর আগে শুরু হওয়া ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া এখনও নীরবে চলছে। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণে চারটি প্রধান ভূ –গাঠনিক অঞ্চলে বিভক্ত।
যথা টেথিস হিমালয়, বৃহত্তর হিমালয়(হিমাদ্রি হিমালয়), ক্ষুদ্রতর হিমালয়(হিমাচল হিমালয়) এবং অব-হিমালয়/ শিবালিক। এই অঞ্চলগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন ভূ- প্রাকৃতিক এবং শিলাস্তরীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। হিমালয়ের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিক ভালদিয়া “সিন্ধু স্যুচার জোন” বলে চিহ্নিত করেন, যেখানে ভারতমহাসাগরীয় পাত ইউরেশিয়ান পাতের নীচে অবনমিত হয়েছে। এই চারটি অঞ্চলকে আলাদা করেছে বড় বড় ভূ-গঠনিক চ্যুতিরেখা। যেমন: টেথিস ও বৃহত্তর হিমালয়ের মাঝখানে রয়েছে সাউথ টিবেটান ডিটাচমেন্ট ফল্ট (STDF), বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর হিমালয়ের মাঝে রয়েছে মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট (MCT), ক্ষুদ্রতর ও অব-হিমালয়ের মাঝে রয়েছে মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট (MBT), এবং অব-হিমালয় বা শিবালিক ও সিন্ধু-গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র সমভূমির মাঝে রয়েছে মেইন/হিমালয়ান ফ্রন্টাল থ্রাস্ট (MFT/HFT)। এগুলো সবই যুক্ত হিমালয়ান ডেকলেমেন্ট নামে এক গভীর চ্যুতি/ ফাটলের সাথে।
ভালদিয়ার গবেষণার শুরু ১৯৬০-এর দশকে, কুমায়ুন অঞ্চলের (হিমাচল ও নেপালের মাঝামাঝি) ভূতত্ত্ব নিয়ে। ১৯৬৪ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।যার একটিতে তিনি কুমায়ুন-গাড়োয়াল এলাকার ক্ষুদ্রতর হিমালয়ের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র, শিলার চরিত্রায়ন এবং স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন।পরবর্তীতে তিনি সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিরূপের গঠন তুলনা করেন।
১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে ভালদিয়া তাঁর গবেষণাতে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি কুমায়ুন ক্ষুদ্রতর হিমালয়ের গঠন, স্তরবিন্যাস ও ভূ-আকৃতির বিকাশ নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৮০ সালে একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করেন—”Geology of the Kumaun Lesser Himalaya”। এটি পরবর্তী প্রজন্মের ভূবিজ্ঞানীদের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক সূত্র হয়ে ওঠে। তিনি পিথোরাগড় জেলার ম্যাগনেসাইট ও ফসফোরাইট খনিজের উৎপত্তিও ব্যাখ্যা করেন।
ভালদিয়া প্রোটেরোজোয়িক যুগের শিলাগুলোকে দক্ষিণের বাইরের বেল্ট ও উত্তরের ভিতরের বেল্টে ভাগ করেন। বাইরের বেল্টে ডামথা-তেজাম গ্রুপ এবং ক্ৰোল সিকোয়েন্স (জৌনসার ও মুসৌরি গ্রুপ) পড়ে। ভিতরের বেল্টে তিনি বারিনাগ, রামগড়, চেইল, ভাটওয়ারি এবং আলমোড়া গ্রুপকে চিহ্নিত করেন। এগুলোকে পৃথক করেছে বিভিন্ন সাব-প্যারালাল থ্রাস্ট —যেমন মুনসিয়ারি, আলমোড়া, বারিনাগ ও রামগড় থ্রাস্ট। এইগুলো একত্রে “রামগড়-মুনসিয়ারি থ্রাস্ট” নামে পরিচিত।
তিনি দেখেন MCT (মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট) তে উত্তরের উচ্চমানের শিলাগুলোর থেকে নিম্নমানের ক্ষুদ্রতর হিমালয়ের শিলাস্তর আলাদা। ভালদিয়া ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি এত বৃহৎ আকারে ক্ষুদ্রতর হিমালয়ের মানচিত্রায়ন করেন। তাঁর এই কাজ পরে নেপালে থাকা হিমালয়ের অংশের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি হিমালয়ের ট্রান্সভার্স স্ট্রাকচারের (আড়াআড়ি গঠন) ওপর একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করেন, যা হিমালয়ের ভূ-গাঠনিক বিবর্তনে তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করে। ১৯৮০ সালে তিনি MCT ও MBT-র বিস্তারিত বর্ণনা দেন।
এরপর তিনি তাঁর গবেষণার পরিধিকে কুমায়ুন-গাড়োয়ালের গ্রেটার ও টেথিস হিমালয় অঞ্চলে প্রসারিত করেন। তিনি ট্রান্স-হিমাদ্রি থ্রাস্ট (বা মালারী থ্রাস্ট) নামে একটি গঠন চিহ্নিত করেন যা বৃহত্তর ও টেথিস হিমালয়ের সীমানা নির্দেশ করে। পরে এটিকে সাউথ টিবেটান ডিটাচমেন্ট সিস্টেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
১৯৮৪ সালে তিনি হিমালয়ের গাঠনিক বিবর্তনকে চারটি ধাপে ভাগ করেন:
1.কারাকোরাম পর্যায় (পরবর্তী ক্রিটেশিয়াস- প্যালিওসিন)
2. মাল্লা জোহর পর্যায় (পরবর্তী ইওসিন-অলিগোসিন)
3. সিরমুরিয়ান পর্যায় (মধ্য মায়োসিন- প্লায়োসিন)
4. শিবালিক পর্যায় (পরবর্তীপ্লায়োসিন-মধ্য প্লিস্টোসিন)
১৯৯০-এর দশকে ভালদিয়া হিমালয়ের ভূমিকম্প প্রবণতা, ভূমিধস ও বন্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি হিমালয়ের পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করে ভূ-গাঠনিকভাবে সক্রিয় অঞ্চলে টেকসই বাড়ি-ঘর নির্মাণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও তিনি নিও-টেকটনিক (আধুনিক ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া) নিয়ে কাজ করেন এবং হিমালয়ের পরবর্তী কোয়াটারনারি পর্বের থ্রাস্টের পুনরায় সক্রিয় হওয়ার প্রমাণ দেন। ভূগোল ও ভূ-তত্ত্বের ভাষায় “Thrust” হলো এক ধরনের বিপরীত ভূগাঠনিক ফাটলরেখা যার মাধ্যমে ভূত্বকের একটি অংশ অন্য একটি অংশের উপর ঠেলে উঠে আসে। এটি সাধারণত কম-কোণ বিশিষ্ট এবং বিপুল চাপ বা টেকটোনিক শক্তির ফলে তৈরি হয়।
তিনি বৈদিক সরস্বতী নদী নিয়েও লেখেন। তাঁর মতে, প্রাচীন সরস্বতী নদী ছিল শতদ্রু ও যমুনার মিলিত প্রবাহ এবং এটি মূলত শিবালিকে অবস্থিত ঘগ্গর নদী ও তার উপনদীগুলির পথ ধরে প্রবাহিত হয় । হরপ্পা সভ্যতার (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০০-৪১০০) ৭৫% নিদর্শন এই প্রাচীন নদী উপত্যকায় পাওয়া যায়। তিনি সরস্বতী নদীর বিলুপ্তির জন্য বেশ কয়েকটি কারণকে চিহনিত করেছেন, যেমন পশ্চিম ভারতের শুষ্ক আবহাওয়া, আরাবল্লী ও হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তন।
হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের ফলে শতদ্রু ও যমুনা নদী যথাক্রমে পশ্চিমমুখী ও পূর্বমুখী পথে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক সরস্বতী নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত ভালদিয়ার করা পুনঃ-অনুসন্ধান, এর প্রাচীন নদীখাত ও সংশ্লিষ্ট জনবসতি শনাক্ত করা, বিলুপ্তির সময়কাল ও কারণ নির্ধারণ, এবং উত্তর ভারতের জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের উপর এর প্রভাব—সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার ভূ-পুরাতত্ত্বের এসব বিষয়কে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার আধার হিসেবে সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
তিনি তাঁর গবেষণার জীবনের শেষ পর্যায়ে ধারওয়ার ক্রেটনের আধুনিক ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া , সাহ্যাদ্রি পর্বতমালা এবং মাইসোর মালভূমি নিয়ে কাজ করেন। এটি মহাদেশীয় শিলা দ্বারা গঠিত একটি স্থিতিশীল ভূখণ্ডের মূল অংশ হিসাবে পরিচিত যেখানে ভূ- গাঠনিক কার্যকলাপ কম হয়। তিনি দেখান পশ্চিম ঘাট, মহাদেবেশ্বরমালাই এবং বিলিগিরিরঙ্গন পর্বত ভূ- গাঠনিক চ্যুতির কারণে গঠিত। এই চ্যুতিগুলি যে পরবর্তী প্লিস্টোসিন যুগ থেকে মধ্য হলোসিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, সেই ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণ পাওয়া যায় ফল্ট-সীমাবদ্ধ রিজ জুড়ে গভীর খাত ও জলপ্রপাত, নদী ও খালের উল্টোমুখে মোড় নেওয়া বাঁক (hairpin loops) বরাবর প্রবাহের দিক পরিবর্তন, ফল্ট অতিক্রম করার সময় নদীর জল জমে থাকা, সমতল খাড়া ঢাল (planar scarps) এবং ত্রিভুজাকার ঢালু অংশ (triangular facets) থেকে। এছাড়াও, তিনি শনাক্ত করেন যে ক্যামব্রিয়ান পূর্ববর্তী যুগের প্রাচীন কয়েকটি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকের রিভার্স ফল্ট ও শিয়ার জোন পরবর্তী কোয়াটার্নারি যুগে পুনরায় সক্রিয় হয়েছিল, যার ফলে নীলগিরি ও আন্নামালাই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।
কে. এস. ভালদিয়ার গবেষণার পরিসর হিমালয়ের প্রায় সব ভূগাঠনিক অঞ্চল, ভূ-প্রক্রিয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি তাঁর দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন: “The Making of India: Geodynamic Evolution” এবং “Neotectonism in the Indian Subcontinent: Landscape Evolution. ” e দুটি বই ভূবিজ্ঞানীদের জন্য অমূল্য সম্পদ।
সূত্র:
01) Khadg Singh Valdiya by SK Tandon ; Resonance Journal ; Indian Academy of Science (2021).
02) Geologist Valdiya honored by The Tribune(11 May, 2015).
03) The Journey of a Foot-Soldier Geologist by Jaishri Sanwal(JNCASR) ; Journal of Science Education (March, 2021).
