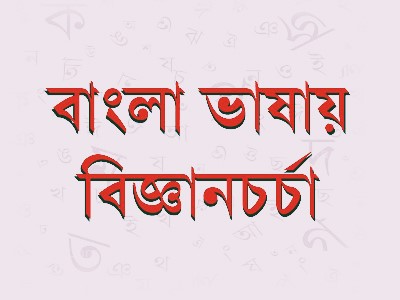
বিজ্ঞানভাষ, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অঙ্গন। যে কোন বিষয়কে নেড়ে চেড়ে, তাকে কাদার তাল থেকে একটা মনের মতন আকার দিতে গেলে, আঙিনা যদি মাতৃভাষার বিচরণভূমি হয়, তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে! কোষ্ঠকাঠিন্যে ভরা বিজ্ঞানকে আপামর বাঙালি পাঠক, বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবে এই হল উদ্দেশ্য।
তবে ভাবনা এলেই তো হলনা, তাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে লাগবে ভাষা- পরিভাষার দখল। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে, প্রথম ও প্রধান অসুবিধা, আমার মতে, পরিভাষার অভাব। এই ব্যাপারটা ইংরেজ আমলের অনেক মনিষীদের মাথাতে এসেছিল, এবং তখন থেকেই বেশ কয়েকজন সেইমত ব্যবস্থাও তাঁরা নিয়েছিলেন।
স্বাধীনতা- পূর্ববর্তী সময়
শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী – পরিভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর । সেই সময়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-নির্ধারণ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়। পরিষদও সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। তার সুত্র ধরেই ত্রিবেদী, ১৩০১ বঙ্গাব্দে, ‘বিজ্ঞান পরিভাষা’ নামের এক প্রবন্ধ লেখেন। বিজ্ঞানের ভাষা যে প্রচলিত ভাষা থেকে আলাদা, এটা তিনি স্পষ্ট করে বলেন- “বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা না হইলে, বিজ্ঞান পুষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পায়না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটেনা।” তিনি, প্রয়োজনে ইংরাজী শব্দকে অনুবাদ না করে সেই শব্দকে সরাসরি গ্রহণ করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সবসময় সরাসরি ইংরাজী শব্দকে ব্যবহার করা কাম্য বা যুক্তিযুক্ত কোনটাই নয়। পাশাপাশি সংস্কৃত শব্দ এবং ‘খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা’-র ব্যবহার করে পরিভাষা তৈরীর কথা বলেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন, mass, force, stress, strain, spin, torque, pressure, tension, flux, power, work – ইত্যাদি ইংরাজী শব্দগুলোকেই পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার কিছু কিছু শব্দ চলতি বাংলা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।
প্রসঙ্গ বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন –
১৩১৫ বঙ্গাব্দে, রাজসাহীতে ‘বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন’-এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম যে প্রস্তাব নেওয়া হয় তা এই পরিভাষাকে কেন্দ্র করেই। প্রস্তাবটি ছিল এইরকম- “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের একটি সমিতি গঠিত হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সমিতির কার্য্য করিবেন। তাঁহারা অবশ্যক মত, সমিতির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশ্চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত (সম্পাদক)” । বিশেষজ্ঞের সমিতি একটা বই প্রকাশ করেছিল- রাসায়নিক পরিভাষা নিয়ে।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়
বিজ্ঞান-পরিভাষা নিয়ে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা চলেছে আর চলছে। এই প্রসঙ্গে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য গঠনের পক্ষে ভাষার কাঠামো’ নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে এক জায়গায় তিনি লেখেন, “…………আজ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানসাহিত্য গঠিত হতে পারেনি তার প্রধান কারণ এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহের অভাব।…………”। কথাটা বহুলাংশে সত্যি। আমরা অনেকেই মনে করি, বিজ্ঞান বিষয়টা ইংরাজী ছাড়া পড়া যাবেই না! কাজেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা কি হতে পারে, সেই নিয়ে একটা চলমান গবেষণা চলছিল আর এখনও চলছে। এ কথা ভীষনভাবে সত্যি, কোন বিষয়কে আত্মস্থ করতে হলে মাতৃভাষা ছাড়া সেই সুযোগ পাওয়া যায় না। আর পরিভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে একটা নির্দিষ্ট শব্দ/শব্দবন্ধ একই বস্তুর পরিচয় বহন করে।
যে উদ্যোগ স্বাধীনতার আগে নেওয়া হয়েছিল সেটা হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলল কেন!!- সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।
কিছু ক্ষেত্রে চিন্তার ভাঁজ
এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, একটা বিষয় বোঝাতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন শব্দ/শব্দবন্ধ ব্যবহার লেখকদের একটা নির্দিষ্ট জিনিস বোঝাতে, একজনের থেকে অন্যজনের ক্ষেত্রে তার অর্থ-পার্থক্য ঘটছে। পরিভাষা নির্বাচনে অনেকসময় অবৈজ্ঞানিক হতে হচ্ছে।
ভাষা কঠিন হওয়াতে, পাঠক পড়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। অথচ বিদেশে ঠিকঠাক পরিভাষা ব্যবহারের ফলে সেই ভাষায় পড়ার উৎসাহ পাঠকের বজায় থাকছে। অনেক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষার পত্রিকাতেই দেখা যায়, ইংরাজী ভাষার পাশাপাশি সেই দেশের ভাষায় পুরো লেখাটা না হোক, অন্তত সারাংশ লেখা থাকে।
যে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ- নির্দিষ্ট বই, পত্রপত্রিকার অভাব। কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যদি বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে হয়, তাহলে সহযোগী বই বা পত্রপত্রিকা দরকার। তবে এক্ষেত্রে, বইগুলো ইংরাজীতেই বেশি পাওয়া যায়। তার সাথে সাথেই নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের বড়ই অভাব। দেখুন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আরো কিছু নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার যেখানে, ইতিহাস (সেটা বিজ্ঞানের ইতিহাসও হতে পারে), সাহিত্য এবং আরো কিছু বিষয়ের আকর গ্রন্থ, পুস্তিকা পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার বিষয়ে খোঁজখবরের জন্য সেরকম কোন গ্রন্থাগার নেই। ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীগুলোর ব্যবহার অতি সীমিত; কেবলমাত্র সেখানকার কর্মচারী, গবেষক, অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট। আর অন্তর্জালে সব সাইটগুলোর ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়না। অনুমতির জন্য যে টাকা লাগে তা একজন ব্যক্তির পক্ষে মেটানো সম্ভব না। বইয়ের দামও অনেকক্ষেত্রে অনেক বেশি। ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরী নামে আই আই টি (খড়গপুর) একটা ডিজিটাল লাইব্রেরীর প্ল্যাটফর্ম আছে। কিন্তু সেখানেও নতুন বিজ্ঞান বই, প্রবন্ধের অভাব আছে।
বর্তমানে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর রমরমা , শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়। সারা ভারতবর্ষেই দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের একটা বক্তব্য মনে করাচ্ছি। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে তিনি বলেছিলেনঃ “পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে গেলে ইংরাজীমাধ্যম স্কুল অপরিহার্য, এই ধারনা বর্তমানে সাধারনভাবে গৃহিত। প্রকৃতপক্ষে, শহরাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে, ইংরাজীর ‘আক্রমণে’ স্থানীয় ভাষা বিপন্ন বোধ করছে”।
এ কথা তো বহুলাংশে সত্যি। বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এমনকি শিক্ষক এই ইংরাজী আক্রমণে নিজেদের ক্ষুদ্র মনে করেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক ও পাঠকের সংখ্যা দিনের পর দিন কমা – ইংরাজী ‘আক্রমণ’-ই এর অন্যতম বড় কারণ। এটা যেন দ্বিতীয় উপনিবেশিকতা! আমরা, অতিসচেতন অভিভাবকরা, যাঁরা সন্তানদের প্লে-স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা তার পর অব্দি সঙ্গ দিই, তাঁরাও অনেকসময় বাংলা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পড়তে নিরুৎসাহিত করি। ইংরাজী গান শুনতে দেখলে বা ইংরাজী বিভিন্ন লেখা পড়তে দেখলে আমাদের গর্বে বুক ভরে ওঠে। ইংরাজীতে কোন এক বিষয় লেখার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই সন্তানদের যতটা উৎসাহিত করি, বাংলা লেখার ক্ষেত্রে, ঠিক ততটাই নিরুৎসাহিত করি। বাংলা ভাষার পাঠক কমার পেছনে আমরা অভিভাবকরাও কিন্তু পরোক্ষভাবে দায়ী।
এই সব প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সমস্যা সমাধানের পথ আমাদেরই খুঁজতে হবে, পরিভাষার এক সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার, বিজ্ঞানের আধুনিক পাঠাগার ভীষণভাবে প্রয়োজন, পরিভাষার প্রয়োজন, উৎসাহের প্রয়োজন, এগিয়ে আসার সাহসের প্রয়োজন। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা, তাঁদের পছন্দের বিষয়ের বই বা জার্নাল সহজেই খুঁজে পান, বিদ্যালয়-স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বাংলায় প্রবন্ধ লেখা, বিতর্কে অংশগ্রহণ করানো প্রবলভাবে জরুরী, আর দরকার কিছু গবেষক-বিজ্ঞানীর ‘বাংলায় লেখক’ হওয়ার।
