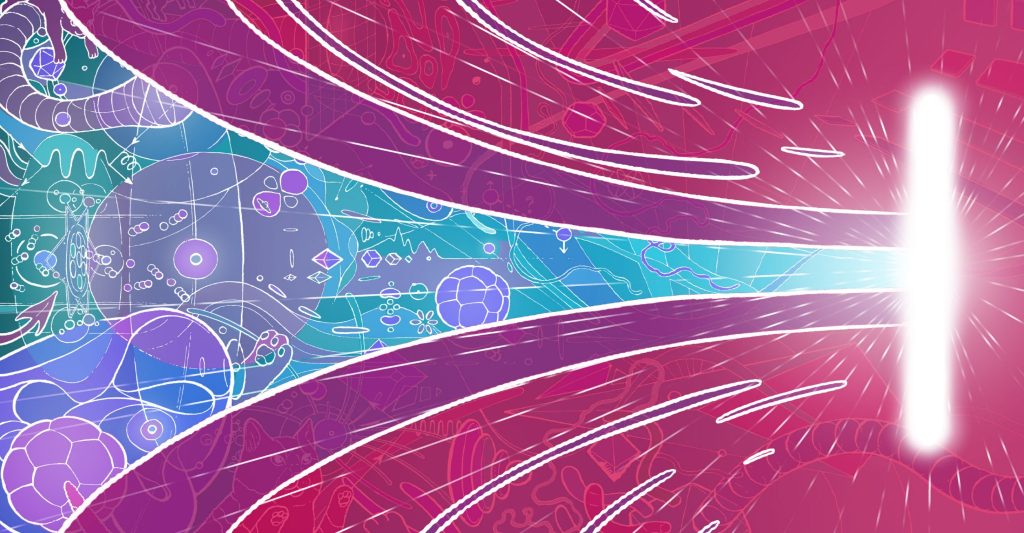
প্রায় একশো বছর ধরে বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান ব্যবহার করছেন। কিন্তু এখনো সে-তত্ত্বটা যে ঠিক কী, তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কিছু বিজ্ঞানী অনেক গভীরে গিয়ে এর ব্যাখ্যা খুঁজছেন। এরই নাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব পুনর্গঠন।
এঁদেরই একজন, হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ গিউলিও শিরিবেল্লা বলেছেন, “আমি দেখাতে চাই, কোয়ান্টাম তত্ত্বই হল একমাত্র তত্ত্ব যেখানে আমাদের অপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলির সাহায্যেই বিশ্বের এক নিখুঁত চিত্র গড়ে তোলা সম্ভব”। কিন্তু এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে শেষ পর্যন্ত যদি তাঁরা কোয়ান্টাম পুনর্গঠনের এই কাজে বিফলও হন, তবু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের চেয়েও গভীর কোনো তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে পারবেন। কানাডার ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী লুসিয়েন হার্ডি বলেছেন, “মনে হয় এ থেকে কোয়ান্টাম গ্রাভিটির একটা তও্বের দিকে এগোনোর ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যাবে”।
আলো এবং অন্যান্য বিকিরণের সঙ্গে অণু আর পরমাণু কীভাবে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় তা বুঝতে গিয়েই কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের উৎপত্তি। সাবেকি পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের গাণিতিক সূত্রগুলি খুবই মজবুত। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পর্বে এর উদ্গাতারা সেগুলোকে যেন তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে চটজলদি প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন এরভিন শ্রোয়েডিঙ্গার কোয়ান্টাম কণাগুলির সম্ভাবনা-ভিত্তিক ধর্মগুলি হিসেব করবার জন্য একটা ‘তরঙ্গ ফাংশানে’র কথা বললেন। এই গাণিতিক সূত্রে এই পুরোনো কথাটার প্রতিফলন ঘটল যে কোয়ান্টাম কণাগুলি কখনো কখনো যেন তরঙ্গের মতো আচরণ করে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা কণাকে পর্যবেক্ষণ করার সম্ভাবনা কতটা তা জানতে চাইলে ওই তরঙ্গ ফাংশানের বর্গফল বার করলেই চলবে। পর্যবেক্ষণ-সাধ্য অন্যান্য কণাদের পরিমাপ করার সম্ভাব্যতা কত তা জানতে হলে, তরঙ্গ ফাংশনের উপর অপারেটর নামক একটা গাণিতিক ফাংশন প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এই তথাকথিত নিয়মটা তো ম্যাক্স বর্ন আর শ্রোয়েডিঙ্গারের স্বজ্ঞাপ্রসূত একটা অনুমান বই আর কিছু নয়। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের অনেকটাই যেন এই রকম চটজলদি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কাঠামো যত জটিলই হোক, এ যেন একটা তাপ্পি মারার মতো কাজ। সুস্পষ্ট কোনো ভৌত ব্যাখ্যা বা যৌক্তিকতা এর নেই। আইনস্টাইনের সীমিত আপেক্ষিকতা তও্বের মূলে যেসব স্বতঃসিদ্ধ কাজ করেছে তার সঙ্গে তুলনা করলেই তফাতটা বোঝা যাবে। দুটি সরল ও স্বজ্ঞাপ্রসূত সূত্র ব্যবহার করে আইনস্টাইন কুয়াশা কাটিয়েছিলেন। এক, আলোর গতি ধ্রুব; দুই, পরস্পরের সাপেক্ষে অপরিবর্তনীয় বেগে চলমান দুজন পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়মাবলী প্রযোজ্য। এর ভৌত তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনীয় বিবৃতিগুলি কী? জন হুইলার একবার বলেছিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল কথাটা যদি আমরা সত্যিই বুঝতে পারি, তাহলে সেটা একটা সরল সর্বজনবোধ্য বাক্যে প্রকাশ করা যাবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের পুনর্গঠন নিয়ে ব্যস্ত বিজ্ঞানীরা এখন বোর, হাইহেনবার্গ আর শ্রোয়েডিঙ্গার-এর কাজকর্ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে ওই রকম এক উপলব্ধিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন। এই প্রয়াসে একটি আদি পদক্ষেপ নেন হার্ডি, যিনি তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর সব দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন সম্ভাবনা তত্ত্বর উপর। তাঁর মতে ওইখান থেকেই সুপরিচিত কোয়ান্টাম ভাবনাগুলোকে দানা বাঁধানো যাবে।
সম্ভাবনা তও্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব
তিনি ধরে নিলেন, যেকোনো সিস্টেমকে তার ধর্মসমূহের এবং তাদের সম্ভাব্য মানের একটা তালিকা দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব। এরপর সেই মানগুলিকে একটিমাত্র পর্যবেক্ষণ মারফত সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করার সম্ভাব্যতা বিচার করলেন তিনি। সাবেকি পদার্থবিজ্ঞানে তো তাই হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী একটা কণা তো তথাকথিত দ্বৈত-দশায় থাকতে পারে (সুপারপোজিশন)। যেমন একটি কোয়ান্টাম বিট, যাকে কিউবিট বলে, তা বাইনারি সিস্টেমের মতো হয় ০ নয় ১, এইরকম দশায় থাকে না। কিন্তু কিউবিটকে মাপতে গেলে দেখবেন, আপনি ১ কিংবা ০-এর হিসেবই পাবেন। এই হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রহেলিকা। এ-কে অনেক সময় তরঙ্গ ফাংশানের বিলয় বলা হয়। অর্থাৎ মাপজোক করলে সম্ভাব্য ফলগুলির মধ্যে থেকে কেবল একটি ফলই বেরিয়ে আসে।
এর পর হার্ডি দেখালেন, এইসব সিস্টেমকে বর্ণনা করার সরলতম সম্ভাব্য তত্ত্বটিই হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান। তরঙ্গসম ব্যতিচার (ইন্টারফিয়ারেন্স), বিজড়িত দশা (এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট) প্রভৃতি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকেই এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। হার্ডির এই কাজ কোয়ান্টাম তত্ত্ব পুনর্গঠনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ। এর মূল কথাটি হল, কোয়ান্টাম তত্ত্বের মর্মমূলে প্রোথিত আছে সম্ভাবনা তত্ত্ব। এই পরিমার্গ (অ্যাপ্রোচ)অনুযায়ী, কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটা সামান্যীকৃত সম্ভাবনা তত্ত্ব। এর একমাত্র বিবেচ্য: আউটপুট কীভাবে ইনপুটের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিরিবেল্লা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এইসব সামান্যীকৃত সম্ভাবনা তত্ত্বগুলি যেন ব্যাকরণের বিশুদ্ধ অন্বয় তত্ত্বের মতো। শব্দগুলির অর্থ নির্বিশেষে “ভাষাতাত্ত্বিক অন্বয়” শব্দগুলির বিভিন্ন বর্গ নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই। এখানেও দশা আর পরিমাপের বর্ণনা দেওয়া হয় ওইভাবেই। এ যেন ভৌত তত্ত্বাবলীর অন্বয়। অর্থাৎ কিনা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব পুনর্গঠনের যাবতীয় পরিমার্গর সাধারণ ভাবনাটা হল, একট তাত্ত্বিক সিস্টেমের ব্যবহারকারী সেই সিস্টেমের যাবতীয় মাপজোকের সম্ভাব্য ফলগুলির একটি তালিকা রচনা করে কাজ শুরু করে। সেই তালিকাটাই হল “সিস্টেমটির দশা”। এর অন্যান্য উপাদানগুলি হল সেইসব উপায় যার সাহায্যে সিস্টেমগুলি একটা থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এছাড়া আছে কতকগুলি নির্দিষ্ট ইনপুট থেকে পাওয়া আউটপুটের সম্ভাব্যতা।
দার্শনিক তৎপর্য
ফ্রান্সের সিইএ সাক্লে-র পদার্থবিজ্ঞান-দার্শনিক আলেক্সেই গ্রাঁবোম বুঝিয়ে বলেছেন, এই ক্রিয়াভিত্তিক পরিমার্গে দেশ-কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি কোনো কিছুই বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য কেবল দুই ধরণের উপাত্তর (ডেটা) প্রভেদ। কোয়ান্টাম তত্ত্বকে সামান্যীকৃত সম্ভাবনা থেকে আলাদা করার পথ কী? এর জন্য সম্ভাবনার আর মাপজোকের সম্ভাব্য ফলের উপর বিশেষ কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়। কিন্তু বিধিনিষেধগুলো তো অনন্য নয়। কাজেই বহু তও্বকেই আপাতদৃষ্টিতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে মনে হয়। তার মধ্যে আসলটাকে বেছে নেওয়ার রাস্তা কী? সেটা ব্যাখ্যা করেছেন স্পেনের বাস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মাথিয়াস ক্লেইনমান। তিনি বলেছেন, খুব সম্ভব কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোনো একটা গভীরতর তত্ত্বের একটা আপাত-গ্রাহ্য চেহারা। সাবেকি পদার্থবিজ্ঞান থেকে যেমন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের গরমিলগুলোকে মেলাতে গিয়েই হয়তো নতুন সেই গভীরতর তও্ব্বের উদয় হবে।
(চলবে)
