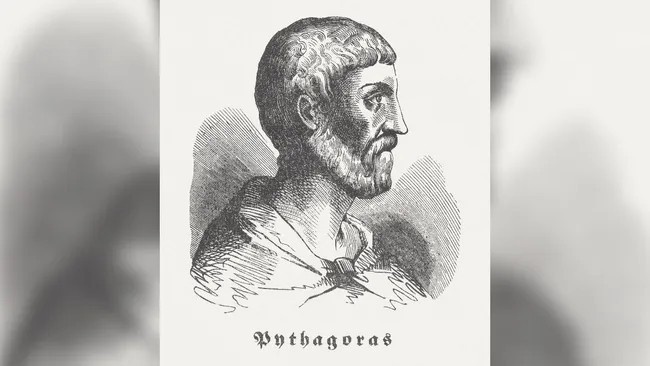
ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জর নানা দ্বীপ; নীলনদ, টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকা; সিন্ধুনদ আর গাঙ্গেয় উপত্যকা আর পীত নদী উপত্যকার পথরেখা ধরে তথাকথিত পিথাগোরাস উপপাদ্যর কত যে প্রমাণ আছে! মেসোপটেমিয়ার কাদামাটির ফলকে রাখা আছে প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের সাক্ষ্য; মিশরীয় ও চৈনিক গোটানো পটেও লেখা য়াছে তার সাক্ষ্য। গ্রীকদের লেখাগুলি আর ভারতের বেদী-নির্মাতাদের সূত্রসমূহ, প্রাচীন কালের জমি-জরিপকার, ভবন-নির্মাতা আর গণিতবিদদের কৃতিত্ব আমাদের অভিভূত করে।
সুতরাং “পিথাগোরাস উপপাদ্য কার আবিষ্কার?’ এই প্রশ্নের উত্তর হলঃ উক্ত উপপাদ্যে বর্ণিত জ্যামিতিক সম্পর্কসূত্রগুলি অনেকগুলি প্রাচীন সভ্যতায় আলাদা আলাদা করে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, সমকোণী ত্রিভুজের তিন বাহুর মধ্যকার সম্পর্কের জ্ঞানটির উদ্ভব হয়েছিল এমন কতকগুলি ব্যাবহারিক সমস্যা থেকে, যে-সমস্যাগুলির সমাধান প্রতিটি সভ্যতার কাছেই খুব জরুরি ছিল। সেটা হল জমি পরিমাপ আর ভবন বা কাঠামো নির্মাণের সমস্যা। তা সে বৈদিক যজ্ঞবেদির মতো অতি জটিল গড়নের কাঠামোই হোক, পিরামিডের মতো অতিকায় কাঠামোই হোক, চীনের বাঁধ আর সেতুগুলির মতো প্রয়োজনসাধক কাঠামোই হোক, কিংবা সমতল মেঝের ওপর খাড়া উল্লম্ব দেওয়াল গেঁথে সরল বাসগৃহ বানানোর সমস্যাই হোক।
এই চিত্রে ভারতের অবস্থান কোথায়? পিথাগোরাস উপপাদ্যর মূল অন্তর্দৃষ্টিটা যাঁরা সবার আগে আয়ত্ত করেছিলেন, ভারতীয় শূল্বকাররা তাঁদেরই এক গোষ্ঠী। এ ব্যাপারে তাঁরা যেমন সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন না, তেমনি আবার মূলস্রোত থেকে পিছিয়েও ছিলেন না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় অনেক সমকক্ষদের মধ্যে তাঁরাও ছিলেন একটি দল। বৌধায়ন আর তাঁর সহকর্মীরা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন অগ্নিময় যজ্ঞবেদির পূত জ্যামিতিতে, এবং পিথাগোয়াস আর তাঁর অনুগামীরা মাথা ঘামিয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে অন্তর্লীন অনুপাত আর তাদের সাম্যসূচক সমীকরণগুলি নিয়ে।
পিথাগোরাস উপপাদ্যের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে পিথাগোরাসের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে যাওয়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। অবশ্যই তার পিছনে কাজ করেছে পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের ইউরো-কেন্দ্রিকতা আর গ্রীস-প্রেমী পক্ষপাত। কিন্তু ইউরো-কেন্দ্রিকতার সঠিক জবাব ভারত-কেন্দ্রিকতা নয়, ইউরো-কেন্দ্রিকতার সঠিক জবাব হল কে-আগে কে-পরে এই খেলাটা একেবারে বন্ধ করা।
কে প্রথম? – এই নিয়ে ধস্তাধস্তিটা নানা কারণে নিষ্ফল। এক, এর দৌলতে বিজ্ঞানের বিবর্তনটা যেন এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস যেন সে-খেলার স্কোর লেখে আর বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদরা যেন তার রেফারি ও বিচারক, বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া যাঁদের কাজ। দুই, এর থেকেও অনেক বড়ো ক্ষতিটা হল, এর দ্বারা প্রাচীন বিজ্ঞান ও তার অনুশীলনকারীদের চিন্তাসংহতিকে আঘাত করা হয়। তাঁদের নিজস্ব অগ্রাধিকার আর পদ্ধতিগুলোকে ঠেসে দেওয়া হয় গ্রীকদের কৃতিত্বের সংকীর্ণ চৌহদ্দিটার মধ্যে।
বৌধায়ন ও অন্যান্য শূল্বকারদের যদি আমরা সত্যিসত্যিই সম্মান জানাতে চাই তাহলে তার অনেক বেশি আন্তরিক এবং সার্থক পথ হল তাঁদের কৃতিগুলিকে তাঁদের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতের সমগ্রতার মধ্যে রেখে অনুধাবন করা, যেসব অভিনব পদ্ধতিতে তাঁরা জটিল স্থাপত্য-ঘটিত সমস্যাগুলির সমাধান করেছিলেন সেগুলি অনুধাবন করা। প্রাচীন ভারতের জ্যামিতিকে শুধুই, এমনকী মূলত পিথাগোরাসসের লেনস দিয়ে বিচার করলে বরং বৌধায়নের প্রতি অন্যায় করা হয়, কেননা শূল্বসূত্রগুলিতে ওই একটি উপপাদ্যর বাইরেও বহু মূল্যবান জিনিস রয়েছে।
পিথাগোরাস নিয়ে আমাদের এই একমুখী আবিষ্টতার অবসান হোক। তাঁকে শান্তিতে বিরাম নিতে দিন।
