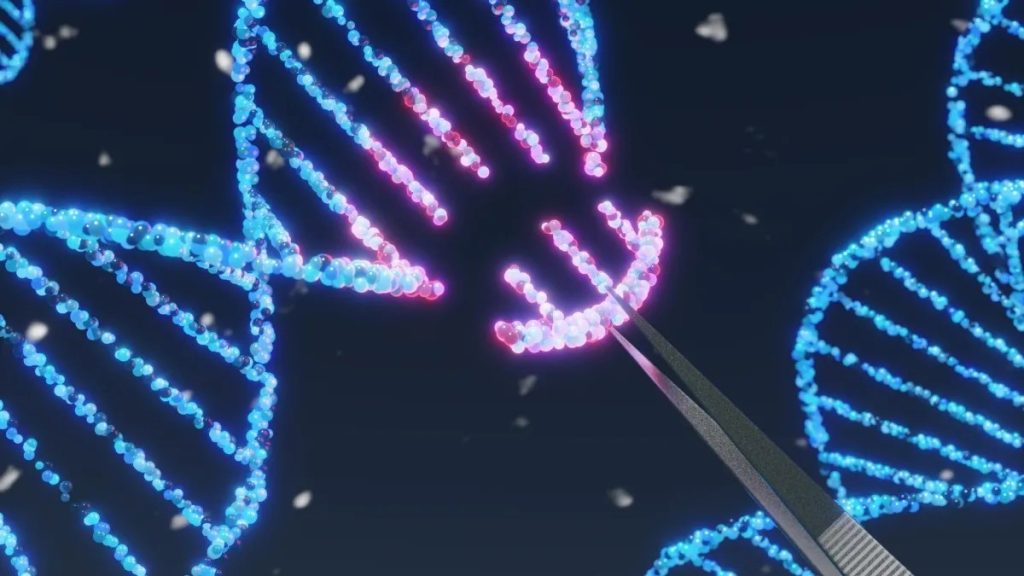
জিন এডিটিং একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে জীবের ডিএনএ-র নির্দিষ্ট অংশ কেটে, বদলে বা সংযোজন করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য তৈরি করা হয়।সহজভাবে বলতে গেলে, জিন এডিটিং মানে হলো জীবের জিন উপাদানে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এনে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে চিকিৎসা, কৃষি, এবং প্রজাতি সংরক্ষণে এটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে শুধু বিপন্ন প্রজাতিগুলিকে সংরক্ষণই নয়, তাদের হারিয়ে যাওয়া জিনগত বৈচিত্র্য ফিরিয়ে দিয়ে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। এমনই মত বিজ্ঞানীদের। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক নমুনা, যেমন – সংগ্রহশালার সংরক্ষিত ডিএনএ ও ঘনিষ্ঠ প্রজাতির জিন – ব্যবহার করে প্রজাতিগুলির হারানো বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন।
ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট অ্যাংলিয়া-র অধ্যাপক কক ভ্যান উস্টারহাউট ও কোলোসাল বায়োসায়েন্সেসের ড. স্টিফেন টার্নারের নেতৃত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক গবেষকদল এই ধারণাটি তুলে ধরেছেন। তারা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বর্তমান পৃথিবীর দ্রুত পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে অনেক প্রজাতির টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিন বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে প্রজাতিগুলির মধ্যে সেই বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
আধুনিক সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টায় আবদ্ধ অবস্থায় বন্যপ্রাণী বা বিপন্ন প্রাণীকে চিড়িয়াখানা বা সংরক্ষণ কেন্দ্রে প্রজনন করানো হয়। এতে আবাসভূমি রক্ষা ও প্রাণী সংখ্যা বাড়ানো গেলেও প্রজাতির ভিতরের জিন বৈচিত্র্য ফেরানো যাচ্ছে না। ফলে এদের জিনগত অবক্ষয় ঘটছে। এরা ভবিষ্যতের পরিবেশগত পরিবর্তন, রোগ কিংবা জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে।
উদাহরণ হিসেবে মরিশাসের গোলাপী পায়রার কথা বলা যায়। এর সংখ্যা মাত্র ১০ থেকে বেড়ে এখন ৬০০-তে পৌঁছেছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে এই প্রজাতির জিনগত অবক্ষয় এতটাই যে, আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে এটি বিলুপ্ত হতে পারে। এই হারানো বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে জিন এডিটিং হতে পারে এক কার্যকর পদক্ষেপ।
বিজ্ঞানীরা জিন এডিটিং এর তিনটি মূল প্রয়োগের কথা বলেছেন। ১) হারানো বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা, ২) মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো (যেমন তাপ সহনশীলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা),
৩) ক্ষতিকর জিনের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর জিন স্থাপন করা।
তবে তারা সতর্ক করেছেন, এই পদ্ধতি এখনো পরীক্ষাসাপেক্ষ, এতে ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি রয়েছে। তাই ছোট পরিসরে পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাবের দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।
পরিশেষে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, জিনএডিটিং কোনো জাদুকরি সমাধান নয়, এটি ঐতিহ্যবাহী সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, যাতে প্রজাতি রক্ষার সম্মিলিত প্রয়াস আরও শক্তিশালী হয়।
সূত্র : Nature Reviews 18/07/2025
