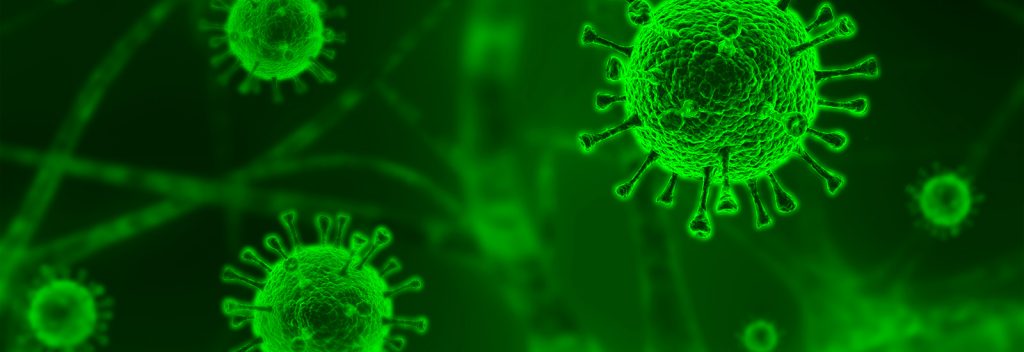
১) ভাইরাস কী?
কোনো বড় বটগাছে বা অশ্বত্থ গাছে শ্যাওলা ধরলে কখনো মনে হয়কি যে ওই শ্যাওলা গাছটাকে শেষ করে ফেলবে, তাহলে এখন অতিমারী বা মহামারী যাই বলুক না কেন শুনে এত ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছেন কেন?
ওই শ্যাওলা যেমন একটা পরজীবী, ভাইরাস্ও ঠিক তেমনই একটা পরজীবী। জীবনে বেঁচে থাকার একটা ন্যূনতম উপাদান হল খাদ্য, আর পৃথিবীর খাদ্যশৃঙ্খ্যলে মোটামুটি দুই শ্রেণির প্রাণি আছে– স্বভোজী আর পরভোজী। স্বভোজী হল গোটা উদ্ভিদজগৎ, বাকি প্রায় সমস্ত জীব্ই পরভোজী, আর পরজীবী হল একপ্রকারের পরভোজী। মানুষ্ও পরভোজী। একটা নিউক্লিক অ্যাসিড আর তার চারদিকে একটা প্রোটিনের বেষ্টনী দিয়ে তৈরি জীব আর জড়ের মধ্যবর্তী স্তরে থাকা প্রকৃতির একটা উপাদান্ই হল ভাইরাস।
মানুষ তো অনেক ভয়ঙ্কর পরভোজী, সে তার খাবারের জন্য পছন্দের প্রাণিগুলিকে ব্যবসায়িক উৎপাদন করে আর তারপরে নৃশংস ভাবে লালসা মেটায়। ভাইরাস তো নগন্য একটা পরজীবী, যে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু প্রাণির শরীরকে তার বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। আর পরজীবীর বৈশিষ্ট্য– সে তার আশ্রয়দাতার শরীর থেকে খাদ্য্উপাদান সংগ্ৰহ করে বেঁচে থাকে, তাই প্রকৃতির নিয়মেই সেই আশ্রয়দাতা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই পরজীবীও শেষ হয়ে যাবে, তাই কখনোই একটা পরজীবী তার আশ্রয়দাতাকে সম্পূর্ণ রূপে মুছে দিতে চাইবে না। তাই ওই প্যানডেমিক, এপিডেমিক যত ভারী ভারী নাম্ই শুনুননা কেন এমন ভয় পাবার কিছু নাই যে পৃথিবী থেকে মানুষ মুছে যাবে।
২) জন্ম
ভাইরাসের জন্ম বা সৃষ্টি বলতে গেলে একটু বিবর্তনের দিকে চোখ রাখতে হবে। সেই সুপ্রাচীন কালে উত্তাপ হ্রাস করে সদ্য ঠান্ডা হ্ওয়া পৃথিবীর বুকে জড় পদার্থ থেকে যখন প্রথম প্রানের হাতেখড়ি হচ্ছে তখন্ই এই ভাইরাসের সৃষ্টি। ভাইরাসের সৃষ্টি মানে সেই প্রথমে H2O, CO2 থেকে জটিল যৌগ তৈরি শুরু, তারপর আরো অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিছুটা সুস্থিত জটিল যৌগ প্রোটিন-কার্বোহাইড্রেট, আর তারপর আরো সুস্থিত আপন প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম ও নিজের পৃথক অস্তিত্ব কায়েমকারী নিউক্লিক অ্যাসিডে্র সৃষ্টি। আরেকটু সহজ করে বললে এই নিউক্লিক অ্যাসিড আর কিছুই না, অনেক যৌগ দিয়ে তৈরি একটা গঠন যেটা তার অধঃস্তন কর্মচারীদের আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, আর এভাবেই তার পৃথক অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।
ভাইরাস ওই নিউক্লিক অ্যাসিডে্র চারপাশে শুধু বৈচিত্র্যময় একটা প্রোটিন বেষ্টনী লাগিয়ে নিয়েছে সামাজিক স্তরে তার মেলামেশার সুবিধার জন্য। মানুষের প্রতিটা কোষেও নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, আর পৃথিবীর প্রতিটা জীবের নিউক্লিক অ্যাসিড স্বতন্ত্র। আর এই ভাইরাস, তারপর আরেকটু জটিল হয়ে ব্যাকটেরিয়া, তার পর ফানগাস, আরও অনেক জটিলতা বাড়তে বাড়তে মানুষ। এতটা সহজ না– বিবর্তনের পথ শতধাবিভক্ত, আমি বিবর্তনের প্রসঙ্গ টানলাম শুধু এটা বোঝাতে যে ভাইরাস একেবারে প্রাথমিক স্তরের একটা উপাদান।
আরো একটা কথা বলার এই ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড অন্যান্য অনেক ভাইরাসের থেকে যথেষ্ট বড় এবং সুস্থিত, তাই এটা গঠন পরিবর্তন (যেটাকে বলা হয় “মিউটেশন”–সহজ কথায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবর্তনশীল প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা; আর যে যত ছোট, যার জটিলতা যত কম সে তত সহজে পারে) করলেও , খুব দ্রুত করতে পারেনা, তাই এর বিরুদ্ধে লড়তে ভ্যাকসিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আর HIV, ZIKA, Ebola আরো কত মারন ভাইরাসের আজও কোন ভ্যাকসিন্ই বের করা যায়নি, তাদের তুলনায় এটা একটা চুনোপুঁটিও না।
এবার একটু COVID-19 এর কথাই আসি,এটা রোগটার নাম; COVID 19 মানে Corona Virus Disease originated বা detected in the year 2019। আর ভাইরাসটার নাম–SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome producing Corona Virus-2) । আর এটা ২ নং কারন আগে একটা ছিল SARS-CoV।
৩) শ্রেণিবিভাগ
ভাইরাসকে মূলত নিউক্লিক অ্যাসিডে্র উপস্থিতির ভিত্তিতে DNA আর RNA VIRUS , এই দুটি শ্রেনিতে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে এটি একটি এনভেলাপ সমন্বিত RNA VIRUS, Coronaviridae family এর অন্তর্গত। এই পরিবারের অন্তর্গত অধিকাংশ সদস্যই আমাদের সাধারণ সর্দিকাশি উপসর্গ আনে। কেবল beta গোত্রের অন্তর্ভুক্ত SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 একটু বাড়াবাড়ি অসুখ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে প্রথম দুটির সাথে আমরা যথাক্রমে ২০০৩ ও ২০১২ তে সম্মুখীন্ও হয়েছি এবং কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়েও উঠেছি যদিও MERS-CoV এর মারনক্ষমতা এটির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এটির সংক্রমন ক্ষমতা বেশি ঠিকই কিন্তু Measles বা Chicken pox এর তুলনায় অনেক কম, আবার মারনক্ষমতাও Birdflu, Ebola, Small pox, HIV এর তুলনায় নগন্য। তবে তা সত্ত্বেও এত দ্রুত প্রসারের কারন হল এর সর্বোচ্চ সংক্রমন ক্ষমতা থাকে উপসর্গ দেখা দেওয়ার ঠিক ২-৩ দিন আগে, তাই মানুষ বুঝতেই পারেনা আর সতর্ক হওয়ার সময়টাও পায়না।
৪) গঠনশৈলী
ভাইরাসের সাধারণ গঠন ওই নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিনবেষ্টনী আর সাথে অনেকের একটা অতিরিক্ত খাম বা এনভেলাপ থাকে। এই প্রোটিনবেষ্টনীতেই অনন্য কিছু গঠন থাকে যা এটিকে সুন্দর ভাবে বন্ধুর মতো মিশে তার আশ্রয়দাতার শরীরে পরজীবীত্ব স্থাপনে সাহায্য করে। এর মধ্যে আছে S-protein( spike), M-protein( membrane), E-protein( envelope), N- protein( nucleocapsid), NS- protein ( nonstructural )….এর মধ্যে S – protein ই এই ভাইরাসকে আমাদের শরীরে ACE-2 Receptor এর সাথে কথা বলে ঢুকতে সাহায্য করে। আর এই ACE-2 মূলত আমাদের ফুসফুসে থাকলেও কম পরিমাণে আমাদের খাদ্যনালি(digestive tract), শ্বাসপথ( respiratory tract),বৃক্ব( kidney), heart, জ্বিহা(Tongue) তেও থাকে। তাই জ্বর-সর্দি্র সাথে সাথে গন্ধ চলে যাওয়া, স্বাদ না পাওয়া, পেটের সমস্যা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।
৫) রোগসৃষ্টির কৌশল
এটা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই জটিল, আমি তার নতুন চমকপ্রদ কিছু কৌশল শুধু তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। প্রথমে ওই ACE-2 Receptor দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। বাকিটা পূর্ণমাত্রায় দু’পক্ষের মুখোমুখি যুদ্ধের সমতুল্য, একদম সহজ কথায় বলার চেষ্টা করছি।
এক অজানা দেশ, দেশটা বেজায় বড়ো, দিগন্তবিস্তৃত ব্যাপ্তি তার, সংগত কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলোর চক্ষুশূল, তবে দেশের সুরক্ষাব্যবস্থা খুবই মজবুত, তাই প্রতিবেশীরা সহজে কিছু করতে পারেনা। দেশের সুরক্ষাকাঠামো মোটামুটি দুই ধাপে বিন্যস্ত, বাইরের ধাপে, মানে যারা সরাসরি সীমানায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে, তারা বেশ শক্তিশালী কিন্তু বোধবুদ্ধি কম, আর কেন্দ্রে থাকে দক্ষ, বুদ্ধিমান সৈন্যসামন্ত। কেন্দ্রের সৈন্যসামন্ত একদম অত্যাধুনিক উপায়ে যুদ্ধ করে, তারা আগে অসংখ্য গুপ্তচর মারফত শত্রুর অবস্থান জানে তারপর তার ক্ষমতা, কৌশল বিচার করে, তারপর যুদ্ধশালায় নিজেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেয়, তারপর সমস্ত আঁটঘাট বেঁধে সম্মুখসমরে নামে। কিন্তু সীমান্তের সৈনিক গুলো যেমন ক্ষমতাশালী তেমনই আনাড়ি আর গোঁয়ারও বটে, তারা শত্রুকে প্রথমে নিধন করতে পারলে ভালো, আর নাহলে এমন ক্ষেপে যায় যে নিজেদেরই হুঁশ থাকেনা, শত্রুদের মারতে গিয়ে এত নিরীহ জনগণ আর সহযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি করে যে, তারাই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন।
শত্রুগুলোও ভারী বিচিত্র, তারা প্রথমেই নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ করেনা, তারা তাদের খর্ব বহিরাকৃতি দিয়ে ওই বোকা সৈনিকদের ঠকায়, তারপর এমন সুকৌশলে এক এক করে দেশের জনগণ মারতে থাকে যে তার পাশের বাড়ির লোকেও সেসব কিছু টের পায়না আর সৈন্যসামন্ত নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়। এইসময় আবার যদি ওই প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশগুলো আক্রমন করে তাহলে তো আর কথাই নাই। এই শত্রুগুলো আবার এমন চালাক, কখনও কখনও তারা ওইসব সৈনিকদের সাথে মিশে তাদের এমন বশ করে ফেলে যে উল্টে তারা নিজেদের সহযোদ্ধাদেরই মারতে থাকে। এইসময় কোনক্রমে গুপ্তচর মারফত, কেন্দ্রের বুদ্ধিমান সৈন্যরা খবর পেয়ে গেলে সামলে নেয় সবকিছু আর যদি খুব দেরি হয়, তাহলে দেশটাই শেষ হয়ে যাবে।
শত্রুগুলো এমনই আশ্চর্য ক্ষমতাশালী যে, একটার পর একটা সৈনঘাঁটি নিঃশব্দে ধ্বংস করে চলে, অথচ সেনাপ্রধানরা কিছু জানতেও পারেনা, আর তারা যখন জানতে পারে তখন আধা শ্মশানে পরিণত দেশের কিছু জীবিত সৈনিকের যথারীতি মগজধোলাই হয়ে গেছে আর কিছু গোঁয়ার সৈনিক গাগলের মতো তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে দেশটাকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। আর সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন বাইরের দেশ থেকে সেনা এনে নিজেদের সেই উন্মত্ত সেনাদেরই আগে মারতে হয়।
এখন এই শত্রুদের ঠেকানোর সবচেয়ে সহজ রাস্তা হল এদের কোনোভাবে ঢুকতে না দেওয়া আর একান্তই ঢুকে পড়লে দ্রুত সেনাপ্রধানদের সাবধান করা আর তাও না পারলে ওই ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হবে, নিজের সৈন্যদেরই মারতে হবে দেশটাকে বাঁচাতে। সমস্যা আরো,আগে থেকে যদি সেনাকাঠামো খুব শক্তিশালী থাকে, তা যেমন সহজে শত্রুকে ঢুকতে দেবেনা, তেমন একবার ঢুকে পড়লে বিশাল পরিমাণ পাগলা সৈনিকদের সামলানো হবে আরো বড় সমস্যা।
এই দেশটা হচ্ছে আপনার body, শত্রু হচ্ছে corona virus, বাইরের সৈনিক হচ্ছে innate immunity, কেন্দ্রের সৈনিক হচ্ছে acquired immunity, প্রতিবেশী শত্রু দেশগুলো হচ্ছে আরও অসংখ্য জীবাণু, গুপ্তচরগুলো হচ্ছে antigen presenting cells, মুখ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে spleen, সেনাগুলোর “মগজধোলাই”হচ্ছে autoimmunity, আর ভাইরাসটা কিছু interferon তৈরি এমনভাবে বন্ধ করে যে পাশের জীবিত কোশটি তার পাশে থাকা মৃতপ্রায় কোশটি সম্পর্কে কোনো তথ্য্ই পায়না, আর আপনি যখন কষ্ট বুঝতে পারেন তখন অনেক দেরি হয়ে যায় সাধারণত, এটা happy hypoxia র জন্য। আর অধিকাংশ মানুষ মরছে ওই পাগলা সৈন্যবাহিনীর উন্মত্ত গোলা-গুলি ছোঁড়ার জন্য, যেটাকে বলে Cytokine storm । আর এই Cytokine এর জন্য্ই জ্বর, সর্বব্যপী রক্তবাহী নালিকার ক্ষতি এবং সবশেষে হৃৎপিণ্ড সহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সার্বিক অক্ষমতাই মৃত্যু ডেকে আনে।
আরো অনেক কিছু আছে, সবটা এখনও বিজ্ঞানীমহলেই পরিস্কার না, আর আমার কাছে তো নয়ই। কিন্তু আপনার শরীরের প্রতিটা কোশ কি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে, সেটা আশাকরি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।তাই নিয়ম মেনে মাস্ক পরা যাতে শত্রু ঢুকতে না পারে, সামাজিকের থেকেও আমার মনে হয় শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলা প্রয়োজন।ভীত না হ্ওয়া, সাবধান হ্ওয়া, সতর্ক থাকা, সতর্ক করা এবং সর্বোপরি মানসিকভাবে দৃঢ় থাকা অধিক জরুরি।
৬) ভাইরাসের উৎপত্তি
আমাদের পরিবেশে অগণন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রটোজোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, রোগসৃষ্টিও করছে, তারা অনেকেই করোনার থেকে অধিক ক্ষমতাশালীও বটে, তা সত্ত্বেও মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোনো একটি ভাইরাসের এরূপ সুবৃহৎ প্রভাব বিস্তার বোধহয় আগে কেউ কখনো দেখেনি। মনে হতেই পারে যে হঠাৎ এরকম ভাইরাসের উৎপত্তি আর লকডাউন নামক অদ্ভুত একটা প্রতিরোধ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের পেছনে সমাজের মাথা তথা পুঁজিপতিদের নতুন কোন আছিলা রয়েছে কিনা। থাকতেই পারে, লকডাউনের ফলে বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, বহু প্রাইভেট কোম্পানি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নাম করে কাজের সময় সীমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়ে কর্মী সংখ্যা আরও কমিয়ে দিয়েছে, মানুষ আরো অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে, সবগুলিতেই পুঁজিপতিদের মুনাফা। এইসব মোটিভগুলো প্রশ্নাতীত নয়, তবে খুব জোরালো প্রমান ছাড়া চায়নার ওই বিজ্ঞানীদের এরকম এক জঘন্য অপরাধের আসামী বানানো মানবসমাজের নিকটই চরম লজ্জার।
চিনের যে উহান প্রদেশে প্রথম এই ভাইরাসের দেখা মেলে, সেখানে চিনা সরকার WHO ( ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) প্রেরিত দুজন বিজ্ঞানীকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে দেয়নি, চিনের এই অদ্ভুত আচরন মানুষের মনে সম্ভাবনার মেঘকে আরও কিছুটা গাঢ় করে। হয়তো গবেষনাগার থেকে দুর্ঘটনা বশত্ এই ভাইরাসটি মানবসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, এরূপ ঘটনা আশ্চর্য্যের কিছু না, তবে কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না। আর এখন এইসকল অবান্তর প্রশ্নের থেকেও এই মহামারীকে আটকানোর কৌশল নিয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়াই কাম্য।
৭) নিয়ন্ত্রণ প্রটোকল পরিবর্তনের ইতিহাস
কোভিড মহামারীর শুরু থেকে আজ অবধি একে আয়ত্তে আনার নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রতিদিন-প্রতিমুহৃর্তে পাল্টাচ্ছে , একদমই একটা নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে রণকৌশল তৈরি করতে হচ্ছে, প্রতিদিন তার আক্রমনের নতুন কিছু পন্থা আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাই হয়ত প্রতিদিন চিকিৎসা পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। একটু বিস্তারিত আকারে বললে প্রটোকল পরিবর্তনের কারণ গুলিকে মূলত দুটি শ্রেনিতে ভাগ করা যায় —১.আর্থ-সামাজিক ২. বৈজ্ঞানিক ।
বৈজ্ঞানিক কারণটা আন্দাজ করা অনেকটাই সহজ, নতুন তথ্য উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক, তবে এর পেছনে বেশ কিছু সর্বসমক্ষে অপ্রকাশ্য আর্থ-সামাজিক কারন্ও রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে জীবিকানির্বাহ সত্যিই একটা বিরাট সমস্যা , আবার বড়ো বড়ো ফার্মাকোলজিকাল কোম্পানিগুলোর সাথে যেহেতু অনেক মানুষেরই জীবিকা জড়িয়ে আছে, তাই করোনার চিকিৎসা পদ্ধতির বাণিজ্যিকরন্ও ঘটেছে
নিম্নস্তরে খুব অমানবিক আর অবৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে।
উন্নয়নশীল দেশে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রটোকল ঠিক করা বা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তার পরিমার্জন-পরিবর্ধন করা যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য, তেমনই সেই প্রটোকল কতটা নিয়মমাফিক প্রযুক্ত হচ্ছে তার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, তবেই একমাত্র অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার রোধ করা সম্ভব। ফার্মাকোলজিকাল কোম্পানিগুলোর অতিসক্রিয়তা বা অতিসাফল্যকে পরিণত বিচারবুদ্ধি দিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিচার করেই সেগুলোর ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। RNA ভাইরাসের দ্রুত রঙপরিবর্তন স্বভাবজাত ধর্ম, কিন্তু এরকম একটা প্রতিকূল সময়ে অবিবেচকের মতো শুধুমাত্র আপন স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা করা কেবল এই পরিস্থিতিকেই ভয়ঙ্কর করছে না আখেরে এই মহামারীকে আরও দীর্ঘায়িত করছে।
এই মহামারী রুখতে সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ “লকডাউন”ও আজ প্রশ্নের মুখে, ল্যানসেটের মতো নামকরা অনেক জার্নাল্ও একে বায়ুবাহিত বলে দেগে দিয়েছে, তবে ‘আইসোলেশন’ ( মূলত রোগীকে আইসোলেট করা ) কিংবা “কোয়ারেনটাইন” ( রোগীর সংস্পর্শে আসা উপসর্গ বিহীন সুস্থ মানুষদের আলাদা করা) চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন কিছু না, এগুলো নিঃসন্দেহে কার্যকর, তবে এত বৃহৎমাত্রায় প্রয়োগের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক যে ক্ষতি হয়েছে তা এই পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতাকে এক বিরাট প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
৮) চিকিৎসা বা সুশ্রুষা…..
— এটা নিয়ে আমার কিছু বলাটা নিতান্তই ধৃষ্টতা, চারিদিকে অনেক প্রথিতযশা ডাক্তারবাবুরা আছেন, তাদের কাছে সঠিক সময়ে যাওয়া এবং তাদের কথা মেনে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
চিকিৎসার সময়টাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম যখন ভাইরাসের সংখ্যা বেশি তখন অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ খান বা না খান যদি আপনার mild disease হয়, তাহলে এমনিতেই সুস্থ হবেন, এইসময় অযথা steroid খেয়ে নিজের শরীরকে বিব্রত করবেননা। আবার পরের দিকে যখন Cytokine storm হচ্ছে তখন উন্মাদের মতো remdesivir, plasma খুঁজে সময় নষ্ট করাটা চরম মূর্খামির। তখন বাঁচবার একটাই উপায় steroid আর anticoagulant ( UFH/LMWH) । আর একটা কথাও বলি অক্সিজেনের চাহিদাটা ঠিক কত পরিমানের সেটা না বুঝে বাড়িতে O2 দেওয়ার চেষ্টা করলে , তাতে হারিয়ে ফেলা মূল্যবান সময়ের সাথে সাথে মানুষটিকেও হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা বাড়ে। তাই সময় থাকতে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের বেড খোঁজাই উচিত।
আবার চিকিৎসা শেষে অতিরিক্ত steroids খেয়ে নিজের immune system কে একেবারে পঙ্গু করে দিয়ে নিজেকে immunocompromised এ পর্যবসিত করলে, কোভিড পরবর্তী Mucormycosis এর সম্ভবনাও বাড়ে। এটা ছত্রাক ঘটিত( Fungus– এটাও আরেকটি পরজীবী) একটা রোগ । ডায়াবেটিস, স্থূলতা, দু্র্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সহ আরো অন্যান্য সমস্যা থাকা মানুষদেরই এই রোগ হচ্ছে। তাই শুধু কোভিড নিয়ে না ভেবে সার্বিকভাবে আপনার শরীরকে সর্বোপরি আপনার মনকে সুস্থ রাখাটা অনেক বেশি জরুরি।
শ্রী অভীক ভট্টাচার্য কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমবিবিএস-য়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং জেবিএনএসটিএস-য়ের সিনিয়র স্কলার।
