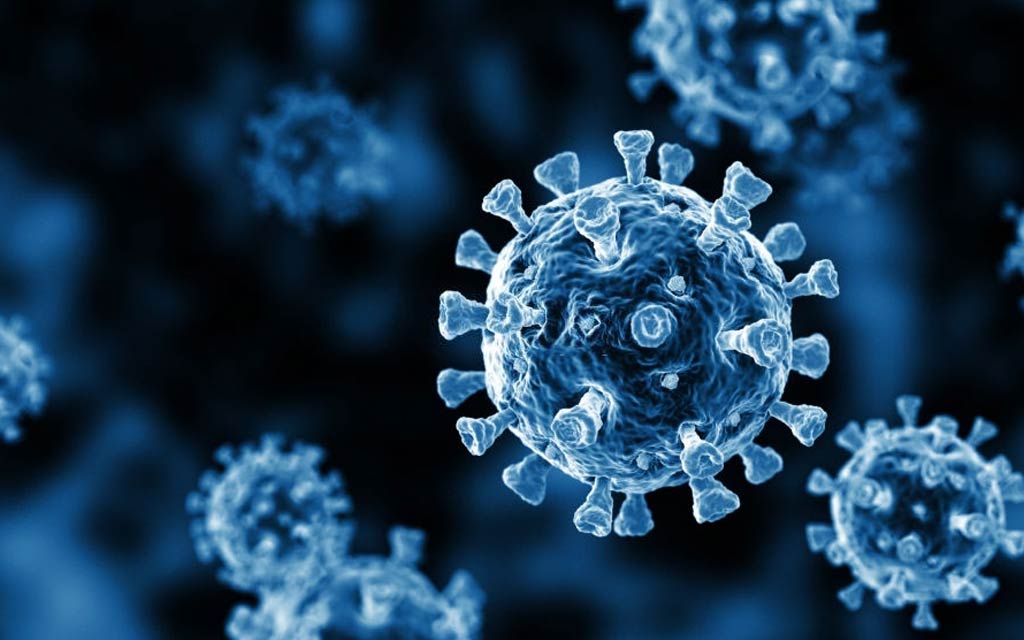
দু’হাজার তেরো সালের পৃথিবী। প্রযুক্তির গর্বে উদ্ধত মার্কিনদেশের এক উন্নত শহর। এক অদ্ভুত অসুখে মানুষ মারা যেতে থাকল। একের পর এক মানুষ। উপসর্গ খুব অদ্ভুত। আক্রান্তের মুখ হয়ে যায় টকটকে লাল, পা আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যায়। উপসর্গ আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান খুবই অল্পসময়ের।
শুরুর দিকে সেভাবে কেউ ভয় পায়নি। মানে, ভয় পেলেও ভরসা ছিল। এত উন্নত দেশ, বিজ্ঞানের উন্নতিও অনেক। নিশ্চয়ই কিছু একটা সমাধান মিলবে। কিন্তু, না, সমাধান মিলল না। মড়কে যাঁরা মারা গেলেন, সেইসব মৃতদেহে অত্যন্ত দ্রুতহারে পচন ধরতে শুরু করল। আর সেই পচা শব থেকে সংক্রমণ আরও ছড়াতে শুরু করল। মৃত্যুপুরী শহর আস্তে আস্তে জনশূন্য হতে শুরু করল। এই জনশূন্য শহর থেকে পালাতে সক্ষম হলেন এক অধ্যাপক।
অনেক অনেক বছর বাদে সেই অধ্যাপক নিজের নাতিনাতনিদের শোনাতে বসবেন ভয়াবহ সে মহামারীর কাহিনী। কেমন করে মানুষের লোভ, যেকোনো মূল্যে মুনাফার জন্যে দৌড় ঘটিয়ে ফেলল এমন মহামারী। কেমন করে সমাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিভাজন শ্রেণীবিন্যাস সংক্রামক ব্যাধিকে মহামারীতে রূপান্তরিত করল। অধ্যাপক জানতেন, সেই অতিমারির শেষে বেঁচে থাকা কতিপয় মানুষের মধ্যে তিনি একজন, তিনিই সেই অতিমারির স্মৃতির শেষতম সংরক্ষক। তিনি যদি বিস্মৃত হন, তাহলে ঠিক কেমন করে কাদের লোভে এমন মহামারী এমন তথাকথিত উন্নত শহরটিকে গ্রাস করে ফেলল, তার কোনো দলিলই থাকবে না। কিন্তু মহামারীর ছ’দশক বাদে, ২০৭৩ সালে বসে, তাঁর নাতিনাতনিরা বুড়ো দাদুর কথা শুনতেই চায় না, তাঁর যাবতীয় স্মৃতির কথাকে অবাস্তব কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়।
হ্যাঁ, এটি জ্যাক লন্ডনের লেখা দ্য স্কারলেট প্লেগ উপন্যাসের গল্প। সে বই ১৯১২ সালে লেখা। গল্পের ভয়াবহতার সাথে না মিললেও তার ঠিক পাঁচ বছর আগেই সানফ্রান্সিসকো শহরে ঘটে গিয়েছে প্লেগ – প্লেগ মহামারি। সেই মহামারী ও তার আর্থসামাজিক কারণ ভেবেই জ্যাক লন্ডন লিখেছিলেন এমন উপন্যাস। আজকের অতিমারীর দিনেও, অতিমারীর ভয়াবহতার পেছনে আর্থসামাজিক কারণগুলো খুব বদলেছে কি?
জ্যাক লন্ডনের বইয়ের তিরিশ বছর আগেই অবশ্য বাংলা উপন্যাসে মহামারীর ভয়ঙ্কর চিত্র উঠে এসেছিল। অবশ্য মহামারী সেখানে পটভূমি – মুখ্য চরিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেখি –
“গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ। মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পালাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে। দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে। অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না।”
এই বিবরণকে অবশ্য অনায়াসেই বর্তমান অতিমারীর লকডাউনের চিত্র বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবে, অতিমারীর ভয়াবহতাই বলুন বা লকডাউনের দাপট (যেটুকু কার্যকরী হয়েছিল), তা কোভিডের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই শহরাঞ্চলে। আনন্দমঠের বিবরণ গ্রামের। বিংশ শতকের গোড়াতে অবশ্য শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে শহুরে মহামারীর জীবন্ত ছবি দেখতে পাই। শুনতে পাই “কেরেন্টিন! কেরেন্টিন!” (কোয়ার্যান্টাইন) ধ্বনি, যা কিনা বর্তমানের খুব কাছাকাছি। পাশাপাশি, ওই বইয়ে শরৎচন্দ্র এক চরিত্রের মুখ দিয়ে যে কথাটুকু বলান, এই অতিমারীর দিনে তা বড্ডো প্রাসঙ্গিক –
“ম্যালেরিয়া, কলেরা, হরেরকমের ব্যাধি-পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদন। কৰ্ত্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান ক’রে নিয়ে যেতে।”
অতিমারীর সঙ্কটের দিনেও আমজনতার যন্ত্রণার প্রতি রাষ্ট্রের নিস্পৃহ থাকা – ব্যাঙ্ক আমানতে সুদের হার কমা ও পেট্রোল-ডিজেল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশ স্পর্শ করা – সরকারের মুখ বদলায়, বদলায় শাসকের চামড়ার রঙও, বদলায় না আমজনতার হয়রানি।
প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক-এ বোম্বাই থেকে কলকাতায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক, গুজবের বাড়বাড়ন্ত – কর্পোরেশনের প্রচার “বোম্বাইসে আদমী আনেসে থানামে খবর দেনা হোগা” – আতঙ্কে মানুষের কলকাতা ছাড়ার প্রয়াস, সেই সুযোগে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়ায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এই বইয়েই আবার কর্পোরেশন টিকা দিতে শুরু করলে পালটা গুজবের কথা পাই – টিকা নেওয়ার দশঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মরে যাচ্ছে – সে গল্পের সাথে তো এই কোভিড টিকাপর্বের আশ্চর্য মিল। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার অবশ্য উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোকে টিকা দিয়ে জনসাধারণের ভয় কাটিয়েছিলেন – বর্তমান স্বাধীন ভারতের সরকার বাহাদুর ঢালাও গুজব মোকাবিলার কোনও প্রয়াসই সেভাবে করলেন না।
সমকালকে ভবিষ্যতে ফেলে, তার অব্যবস্থা-অসঙ্গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে যে ভয়াবহতার ছবি দেখিয়েছিলেন জ্যাক লন্ডন – এদেশের মানুষের অসহায়তাকে উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করে যে বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্র, (পরবর্তীতে বিভূতিভূষণ বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও) – সেই রাষ্ট্রীয় নিস্পৃহতার বিপরীতে মানুষ হিসেবে মানুষের হাত ধরার বাস্তবতাও ছিল। যেমন কিনা রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ উপন্যাসে সংক্রামক অসুখের আতঙ্কে আক্রান্তকে ফেলে পালানোর বিপরীতে – “ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।”
সমাজের সবাই মিলে সবার পাশে না দাঁড়ালে, বিপদ থেকে একা বাঁচতে চাইলে সবসময় বাঁচা সম্ভব হয় না – সংক্রামক মহামারীর বিপদের অভিনবত্ব এখানেই, এখানেই এই বিপদ আর পাঁচটা বিপদ থেকে ব্যতিক্রমী। এই হাতে-হাত রাখা আরও জরুরি, যখন রাষ্ট্র নিস্পৃহ। মুখে বড় বড় কথা না বলে, সকলে মিলে মহামারী মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের মনীষীরাই –
“সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারি চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেক্শনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল।” (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর – জোড়াসাঁকোর ধারে)
এসব গল্পই কমবেশি একশ-সোয়াশো বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে বিজ্ঞান এগিয়েছে অনেক। সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ে, জীবাণু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু সংক্রামক মহামারীর বাস্তবতা কোনো একখানে অপরিবর্তিতই রয়েছে – আমজনতার দুর্ভোগ বিষয়ে শাসকের নিস্পৃহতা কমেছে নাকি বেড়েছে বলা মুশকিল – কিন্তু যেটা একেবারেই বদলায়নি, তা হলো আমাদের আরো বেশি দায়বদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব।
একক ব্যক্তির সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার সাথে সংক্রামক মহামারী/অতিমারীর মোকাবিলা চরিত্রগতভাবেই ভিন্ন। প্রথমটিতে আর পাঁচটা আনুষঙ্গিক বিষয়ের তুলনায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথোপযুক্ত প্রয়োগই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ – কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের দায়িত্ব, সহমর্মিতা ও দায়বদ্ধতার গুরুত্ব প্রায়োগিক বিজ্ঞানের চাইতে বেশী বই কম নয়। প্রশাসন যদি দায়িত্ব বিষয়ে অমনোযোগী হয়, তাহলে সমাজের সকলের দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। আর প্রশাসন ও সমাজ, উভয়ই যদি সঙ্কটকালে নিজ দায়িত্ব বিস্মৃত হয়, তাহলে সেদেশের মানুষের ভোগান্তির একশেষ – নগরের সে আগুনের শিখা থেকে শেষমেশ কোনো দেবালয়ই বাঁচতে পারে না। অতীতই বলুন বা বর্তমান, মহামারী/অতিমারী থেকে টেক হোম মেসেজ হিসেবে কিছু শিখতে চাইলে, এটুকই।
